কৌটিল্যের রাষ্ট্রতত্ত্ব ও চুক্তি ধারণা: Kautilya’s political theory.
ভারতীয় রাজনৈতিক চিন্তার ইতিহাসে কৌটিল্য বা চাণক্য ছিলেন এক যুগান্তকারী চিন্তাবিদ, যিনি রাষ্ট্রনীতি, অর্থনীতি ও প্রশাসনিক ব্যবস্থা সম্পর্কে গভীর দৃষ্টিভঙ্গি প্রদান করেছিলেন। তাঁর রচিত অর্থশাস্ত্র প্রাচীন ভারতের শাসনব্যবস্থার এক মৌলিক নথি, যেখানে রাষ্ট্রের উৎপত্তি, প্রকৃতি, উদ্দেশ্য এবং কাঠামো নিয়ে সুস্পষ্ট আলোচনা পাওয়া যায়। কৌটিল্যের মতে, রাষ্ট্র কোনো দৈব বা প্রাকৃতিক সত্তা নয়, বরং এটি মানবসমাজের চুক্তিভিত্তিক প্রয়োজনে গঠিত এক সংগঠন।
রাষ্ট্রের উৎপত্তি ও চুক্তির ধারণা:
কৌটিল্যের রাষ্ট্রতত্ত্বের মূলভিত্তি ছিল চুক্তি বা সামাজিক সম্মতির ধারণা। তাঁর মতে, প্রাথমিক অবস্থায় মানুষ রাষ্ট্রহীন বা অরাজক সমাজে বসবাস করত, যেখানে “মাৎস্যন্যায়”—অর্থাৎ “বড় মাছ ছোট মাছকে খায়”—এই নীতি প্রচলিত ছিল। এমন অরাজক অবস্থায় শৃঙ্খলা ও নিরাপত্তা পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য জনগণ সম্মিলিতভাবে মনু বৈবস্বতকে রাজা নির্বাচিত করেন। রাজা জনগণের কাছ থেকে উৎপাদনের ষষ্ঠাংশ কর হিসেবে গ্রহণ করেন এবং এর বিনিময়ে তাদের নিরাপত্তা ও কল্যাণের দায়িত্ব পালন করেন।
এই ধারণার মধ্যেই রাষ্ট্রের চুক্তিভিত্তিক উৎপত্তির সূত্র নিহিত। কৌটিল্যের এই ভাবনার সঙ্গে পাশ্চাত্যের দার্শনিক হবস, লক ও রুশোর সামাজিক চুক্তি মতবাদের মিল পাওয়া যায়। তবে তাদের মধ্যে পার্থক্যও ছিল। পাশ্চাত্যের দার্শনিকদের মতে চুক্তি ছিল সামাজিক প্রকৃতির, কিন্তু কৌটিল্যের মতে এটি ছিল সরকারগত চুক্তি—অর্থাৎ শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য সম্পাদিত এক প্রশাসনিক চুক্তি।
কৌটিল্য ও হবস উভয়েই অরাজকতা বা বিশৃঙ্খল সমাজ থেকে মুক্তির উপায় হিসেবে চুক্তির কথা বলেছেন। হবস যেমন রাষ্ট্রকে সর্বশক্তিমান “লেভায়াথান” হিসেবে দেখেছেন, তেমনি কৌটিল্যও রাজার ক্ষমতাকে প্রায় সর্বাধিক মনে করেছেন। এই দৃষ্টিকোণ থেকে বলা যায়, কৌটিল্য ছিলেন হবসের এক প্রাচ্য পূর্বসূরি।
রাষ্ট্রনীতি ও প্রশাসনিক ধারণা:
কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র কেবল রাজনৈতিক চিন্তার দলিল নয়, এটি এক বাস্তববাদী প্রশাসনিক নির্দেশিকা। তিনি রাষ্ট্রকে “সর্ববৃহৎ ব্যবসায়ী” বলে উল্লেখ করেছেন, কারণ রাষ্ট্রই উৎপাদন, কর, রাজস্ব, বিচার ও নিরাপত্তার সর্বময় নিয়ন্ত্রক।
বৃহৎ রাষ্ট্র গঠন:
কৌটিল্য বৃহৎ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পক্ষে ছিলেন। বৃহৎ রাষ্ট্র হলে রাজস্ব বৃদ্ধি পায়, প্রশাসন শক্তিশালী হয় এবং জনগণের কল্যাণ নিশ্চিত করা যায়।
আইনের শাসন ও দণ্ডনীতি:
রাজাই আইনের রক্ষক—এই ধারণা কৌটিল্যের রাষ্ট্রচিন্তার মূলভিত্তি। অপরাধীদের শাস্তি প্রদান ও নিরপরাধদের পুরস্কৃত করা রাজার নৈতিক দায়িত্ব।
মন্ত্রীপরিষদ:
কৌটিল্যের মতে, রাজা মন্ত্রী ও রাজকর্মচারীদের সহযোগিতায় রাষ্ট্র পরিচালনা করবেন। এই পরামর্শ আজকের গণতান্ত্রিক প্রশাসনের প্রাথমিক ধারণার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ।
রাজস্বনীতি:
জমির জরিপ, কর নির্ধারণ ও রাজকোষ পূর্ণ রাখা ছিল কৌটিল্যের অন্যতম নির্দেশ। রাজস্বই রাষ্ট্রের প্রাণশক্তি—এই উপলব্ধি তাঁর অর্থনৈতিক বাস্তববোধের প্রমাণ।
সপ্তাঙ্গ তত্ত্ব:
কৌটিল্য রাষ্ট্রকে জীবদেহের সঙ্গে তুলনা করে সাতটি অঙ্গের কথা বলেছেন—স্বামী (রাজা), অমাত্য (মন্ত্রী), জনপদ, দুর্গ, কোষ, দণ্ড ও মিত্র। এই সাতটি উপাদানের সমন্বয়েই রাষ্ট্র টিকে থাকে।
মণ্ডল তত্ত্ব ও পররাষ্ট্রনীতি:
প্রতিবেশী রাষ্ট্র স্বভাবশত্রু, আর শত্রুর শত্রু স্বভাবমিত্র—এই ধারণার উপর ভিত্তি করে কৌটিল্য পররাষ্ট্রনীতির “মণ্ডল তত্ত্ব” ব্যাখ্যা করেন। তাঁর পররাষ্ট্রনীতিতে যুদ্ধ ও কূটনীতির বাস্তব প্রয়োগের উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।
উপসংহার:
সার্বিকভাবে কৌটিল্যের রাষ্ট্রতত্ত্ব এক বাস্তববাদী ও প্রয়োগমুখী রাজনৈতিক দর্শন। তিনি রাষ্ট্রকে জনগণের ইচ্ছার ফসল হিসেবে দেখেছেন এবং রাষ্ট্রের মূল লক্ষ্য হিসেবে প্রজাদের নিরাপত্তা, শৃঙ্খলা ও কল্যাণকে চিহ্নিত করেছেন। তাঁর অর্থশাস্ত্র কেবল প্রাচীন ভারতের প্রশাসনিক চিন্তাই নয়, আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানেরও এক মৌলিক ভিত্তি। রাষ্ট্র, রাজনীতি ও অর্থনীতির পারস্পরিক সম্পর্ক বিষয়ে কৌটিল্যের দৃষ্টিভঙ্গি আজও প্রাসঙ্গিক ও শিক্ষণীয়।
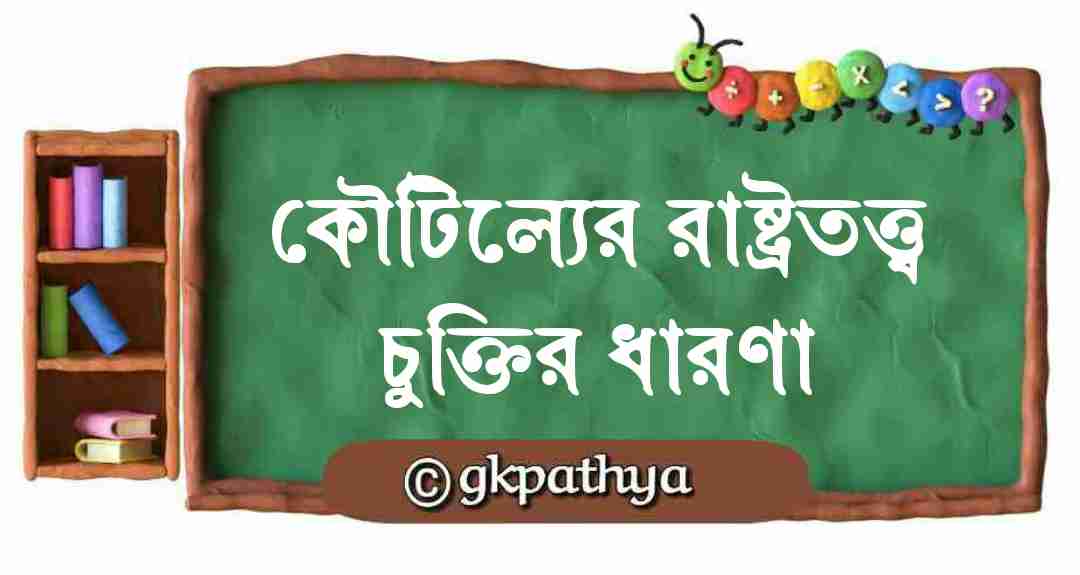
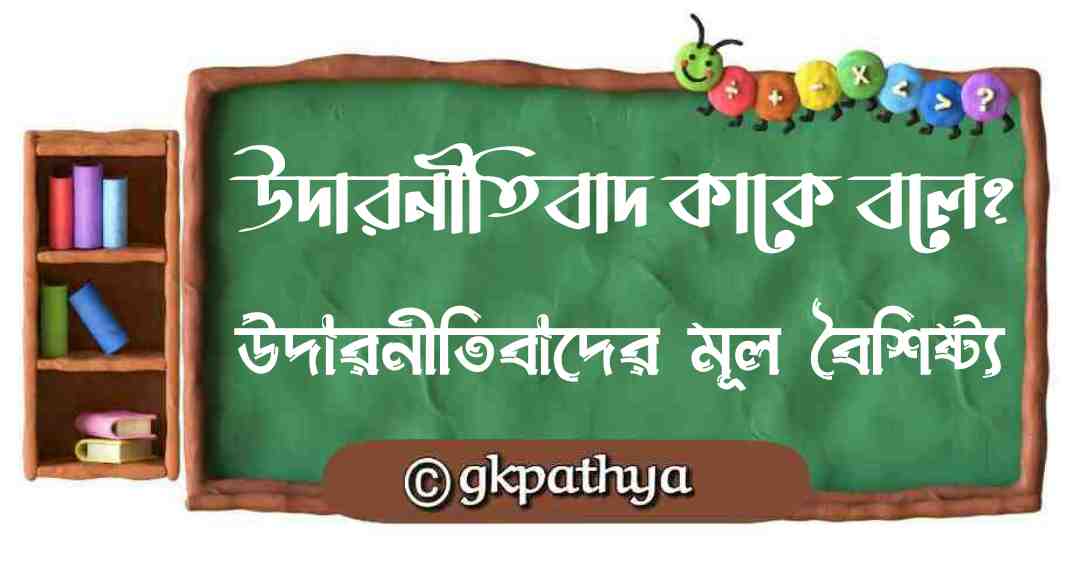
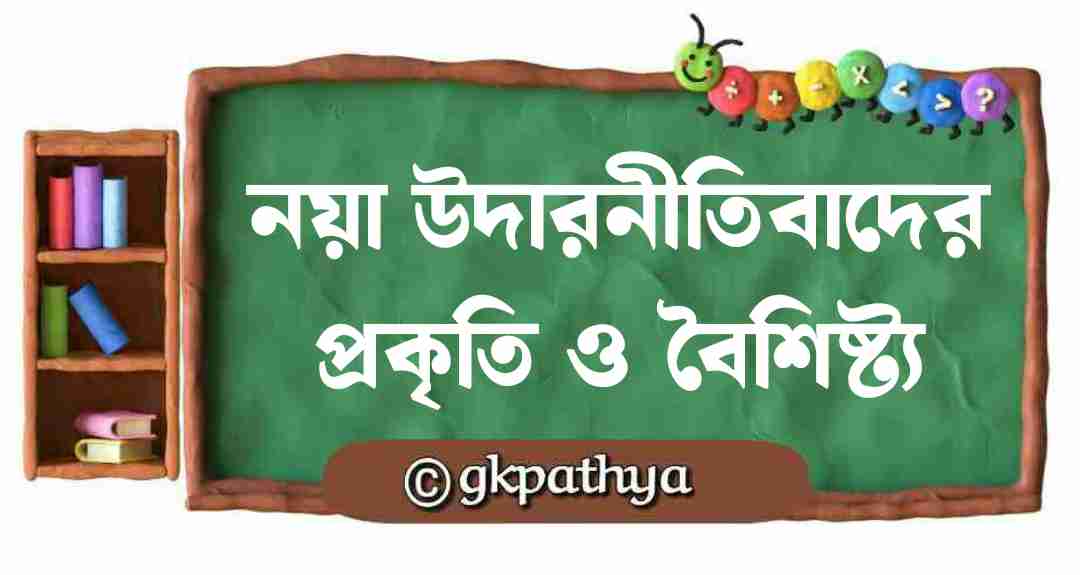

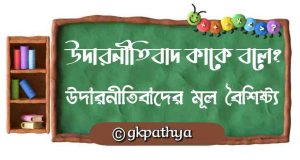
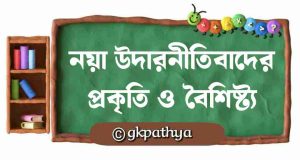

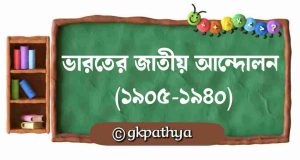
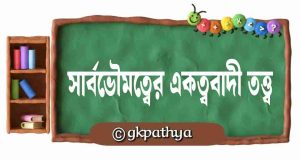
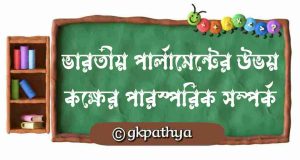
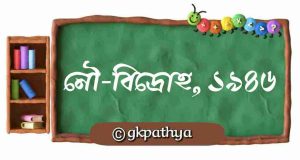


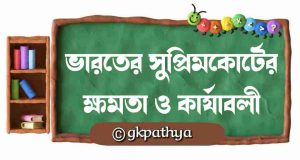
Post Comment