ইক্তা ব্যবস্থা ও তার বিবর্তন | দিল্লি সুলতানি যুগের প্রশাসনিক ব্যবস্থা ব্যাখ্যা: (Iqta System and its Evolution).
দিল্লির সুলতানি যুগে প্রাদেশিক শাসনব্যবস্থার এক অপরিহার্য অঙ্গ ছিল ইক্তা ব্যবস্থা। ইক্তা ছিল এক ধরনের ভূমি প্রশাসন ও রাজস্ব আদায়ের পদ্ধতি, যা সুলতানি প্রশাসনের আর্থিক ও সামরিক ভিত্তি গড়ে তুলেছিল। ইক্তা গ্রহণকারীকে ‘মাকতি’ বা ‘ইক্তাদার’ বলা হত। ‘ইক্তা’ শব্দের অর্থ একটি অংশ বা অঞ্চল। রাজস্ব ব্যবস্থার দিক থেকে এর অর্থ— ভূমি থেকে উৎপন্ন ফসল বা করের ওপর নির্দিষ্ট ব্যক্তিকে সুলতানের পক্ষ থেকে অধিকার প্রদান।
ইক্তা ব্যবস্থার প্রবর্তন:
ইক্তা ব্যবস্থা মূলত ইসলামি জগতে প্রচলিত ছিল। পরবর্তীকালে তুর্কিরা এই ব্যবস্থা ভারতে নিয়ে আসে। ভারতের ত্রয়োদশ শতকের সূচনায় সুলতান ইলতুৎমিস এই ইক্তা প্রথা চালু করেন এবং তা দিল্লির সুলতানি প্রশাসনের মেরুদণ্ডে পরিণত হয়। ইলতুৎমিসের হাত ধরেই এই প্রথা একটি প্রাতিষ্ঠানিক রূপ লাভ করে।
ইক্তার প্রকারভেদ:
সুলতানি যুগে ভূমি মূলত দুই ভাগে বিভক্ত ছিল—
- খালিসা জমি: এই জমির সমস্ত রাজস্ব রাজকোষে জমা হত। এটি ছিল সুলতানের খাস জমি।
- খালিসা বহির্ভূত জমি বা ইক্তা জমি: এই জমি সুলতান নির্দিষ্ট শর্তে তাঁর সেনাপতি, সৈনিক ও অভিজাতদের মধ্যে বণ্টন করতেন। তারা এই জমি থেকে রাজস্ব আদায়ের অধিকার পেতেন, বিনিময়ে সামরিক ও প্রশাসনিক দায়িত্ব পালন করতেন। এই ব্যবস্থাকেই ইক্তা প্রথা বলা হয়।
ইক্তা ব্যবস্থা প্রবর্তনের উদ্দেশ্য
ইক্তা ব্যবস্থা প্রবর্তনের মূল উদ্দেশ্য ছিল—
- সুবিশাল সাম্রাজ্যকে কার্যকরভাবে নিয়ন্ত্রণ করা।
- দূরবর্তী প্রদেশগুলিতে সুলতানের ক্ষমতা বজায় রাখা।
- তুর্কি আমির ও অভিজাতদের সন্তুষ্ট রাখা, যাতে তারা বিদ্রোহ না করে।
- নিয়মিত রাজস্ব সংগ্রহ নিশ্চিত করা।
এ ছাড়া প্রশাসনের প্রতিটি স্তরে কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রেও এই ব্যবস্থা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।
ইক্তাদারদের দায়িত্ব ও কর্তব্য
ইক্তাদাররা তাদের প্রাপ্ত জমি থেকে রাজস্ব আদায় করতেন, কিন্তু তা তাদের স্থায়ী সম্পত্তি ছিল না। তাদের প্রধান দায়িত্ব ছিল—
- সুলতানের প্রয়োজন অনুযায়ী সৈন্য সরবরাহ করা।
- নিজেদের ইক্তা অঞ্চলে আইন-শৃঙ্খলা বজায় রাখা।
- রাজস্ব আদায় করে রাজকোষে জমা দেওয়া।
তারা রাজস্ব থেকে নিজের ব্যয় বাদ দিয়ে অবশিষ্ট অংশ সুলতানের কাছে পাঠাতেন। ফলে ইক্তাদাররা প্রশাসন ও সামরিক শক্তির এক গুরুত্বপূর্ণ অংশ হয়ে ওঠে।
সর্বোপরি, ইক্তা ব্যবস্থা ছিল দিল্লির সুলতানি প্রশাসনের অন্যতম মূল স্তম্ভ। এই প্রথার মাধ্যমে সাম্রাজ্যের রাজস্ব, সৈন্যবাহিনী ও প্রাদেশিক শাসন কার্যকরভাবে পরিচালিত হয়। যদিও পরবর্তী কালে ইক্তাদারদের ক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়ে কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ কিছুটা দুর্বল হয়ে পড়ে, তবুও এটি সুলতানি শাসনের অর্থনৈতিক ও প্রশাসনিক কাঠামোর সবচেয়ে সফল প্রতিষ্ঠান হিসেবে ইতিহাসে স্থান করে নেয়।
ইক্তা ব্যবস্থার সংস্কার ও বিবর্তন:
দিল্লির সুলতানি যুগে প্রাদেশিক প্রশাসনের অন্যতম ভিত্তি ছিল ইক্তা ব্যবস্থা। এটি ছিল এক ধরনের রাজস্ব ও প্রশাসনিক পদ্ধতি, যার মাধ্যমে সুলতান সাম্রাজ্যের বিশাল অঞ্চল পরিচালনা করতেন। ‘ইক্তা’ শব্দের অর্থ অংশ বা এলাকা। সুলতান এই ইক্তার রাজস্ব আদায়ের অধিকার নির্দিষ্ট শর্তে কোনো ব্যক্তি বা কর্মকর্তাকে দিতেন, যাকে বলা হত ইক্তাদার। ইক্তাদাররা রাজস্ব আদায়, সৈন্য সরবরাহ এবং প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব পালন করতেন। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন সুলতানের আমলে এই ব্যবস্থার সংস্কার ও পরিবর্তন ঘটতে থাকে।
ইলতুৎমিসের আমল:
দিল্লির তুর্কি সুলতান ইলতুৎমিস (১২১১–১২৩৬ খ্রি.) ইক্তা ব্যবস্থাকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেন। তিনি প্রথম এই প্রথাকে সংগঠিত করেন এবং প্রশাসনের মূল কাঠামোর অংশ করে তোলেন। ইলতুৎমিস ইক্তাদারদের বদলির নীতি প্রবর্তন করেন, যাতে কোনো ইক্তাদার নির্দিষ্ট এলাকার ওপর স্থায়ী বা বংশানুক্রমিক অধিকার অর্জন করতে না পারে। তাঁর এই নীতির ফলে কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ বজায় থাকে এবং ইক্তাদারদের ক্ষমতা সীমাবদ্ধ থাকে।
বলবনের আমল:
বলবন (১২৬৬–১২৮৭ খ্রি.) ইক্তা ব্যবস্থায় কেন্দ্রীকরণ প্রক্রিয়াকে আরও শক্তিশালী করেন। তিনি লক্ষ্য করেন যে অনেক ইক্তাদার রাজস্ব আদায় করলেও সুলতানকে নির্ধারিত সৈন্য সরবরাহ করে না। ফলে তিনি নিয়ম ভঙ্গকারীদের তালিকা তৈরি করেন এবং প্রতিটি ইক্তায় খোয়াজা নামে হিসাব পরীক্ষক নিয়োগ করেন, যারা রাজস্বের হিসাব ও প্রশাসনিক কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ করতেন। এই পদক্ষেপের ফলে রাজস্ব সংগ্রহে শৃঙ্খলা ও স্বচ্ছতা বৃদ্ধি পায়।
আলাউদ্দিন খলজির আমল:
আলাউদ্দিন খলজি (১২৯৬–১৩১৬ খ্রি.) ইক্তা ব্যবস্থায় মৌলিক পরিবর্তন আনেন। সাম্রাজ্যের আয়তন বৃদ্ধির পর তিনি দিল্লি সংলগ্ন অঞ্চলগুলিকে খালিসা জমি ঘোষণা করেন, যার রাজস্ব সরাসরি রাজকোষে জমা হত। দূরবর্তী প্রদেশগুলিতে তিনি ইক্তা ব্যবস্থা বজায় রাখেন। এছাড়া, সৈন্যদের ইক্তা না দিয়ে নগদ বেতন (Cash Payment System) চালু করেন। এর ফলে সামরিক শৃঙ্খলা ও রাজস্ব প্রশাসনে কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ আরও দৃঢ় হয়।
মহম্মদ বিন তুঘলকের আমল:
মহম্মদ বিন তুঘলক (১৩২৫–১৩৫১ খ্রি.) ইক্তা ব্যবস্থায় অর্থনৈতিক সংস্কার আনেন। তিনি সর্বাধিক রাজস্ব প্রদান করতে ইচ্ছুক ব্যক্তিকে ইক্তার দায়িত্ব দিতেন — একে বলা হত নিলাম পদ্ধতি। একই সঙ্গে তিনি সৈন্যদের নগদ বেতন প্রদানের নীতি অব্যাহত রাখেন। যদিও এই ব্যবস্থায় রাজস্ব আদায়ে স্বচ্ছতা বাড়ে, কিন্তু সাধারণ কৃষকদের ওপর করের বোঝা বৃদ্ধি পায়।
ফিরোজশাহ তুঘলকের আমল:
ফিরোজশাহ তুঘলক (১৩৫১–১৩৮৮ খ্রি.) ইক্তা ব্যবস্থায় ব্যাপক পরিবর্তন আনেন। তিনি ইক্তা বিতরণে উদারনীতি গ্রহণ করেন, ফলে খালিসা জমির পরিমাণ হ্রাস পায়। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন ছিল, তিনি ইক্তাকে বংশানুক্রমিক (Hereditary) করে দেন। অর্থাৎ ইক্তাদার মারা গেলে তার উত্তরাধিকারীরা সেই ইক্তার অধিকার পেতেন। এর ফলে অভিজাত শ্রেণির শক্তি বৃদ্ধি পেলেও কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ দুর্বল হয়ে পড়ে।
উপসংহার:
ইলতুৎমিস থেকে ফিরোজশাহ তুঘলক পর্যন্ত ইক্তা ব্যবস্থায় ক্রমাগত পরিবর্তন এসেছে। প্রথমদিকে এটি কেন্দ্রীয় শাসনকে শক্তিশালী করলেও, শেষ পর্যায়ে বংশানুক্রমিক প্রথার কারণে সাম্রাজ্যের নিয়ন্ত্রণ দুর্বল হয়। তবুও ইক্তা ব্যবস্থা মধ্যযুগীয় ভারতের প্রশাসনিক ইতিহাসে এক অনন্য উদাহরণ হিসেবে গণ্য হয়। এটি ছিল দিল্লি সুলতানি শাসনের অর্থনৈতিক ও সামরিক কাঠামোর প্রধান ভিত্তি, যার উপর নির্ভর করেই সাম্রাজ্যের শৃঙ্খলা, রাজস্ব ও প্রাদেশিক প্রশাসন টিকে ছিল।
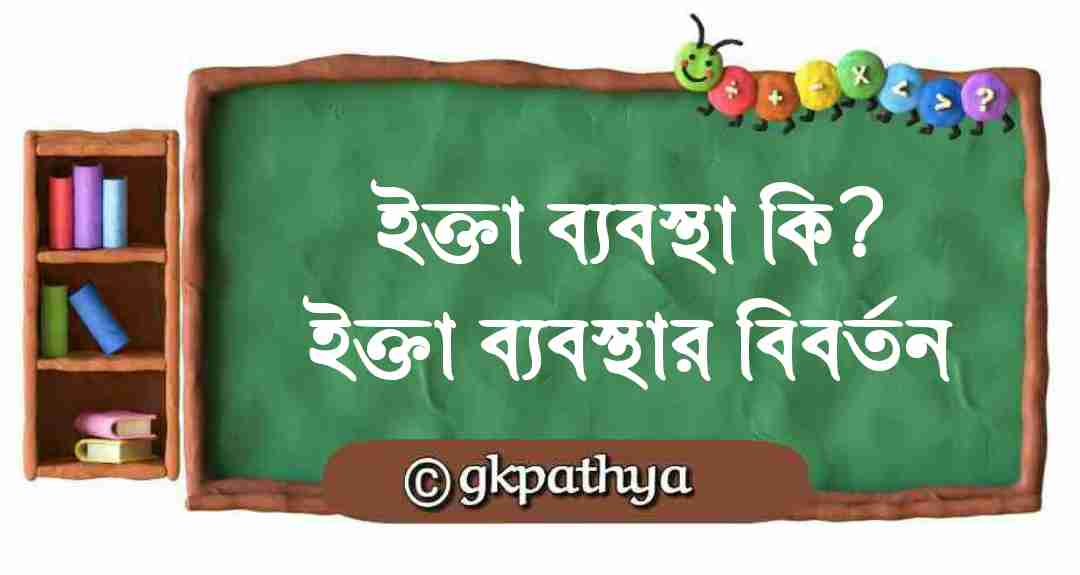
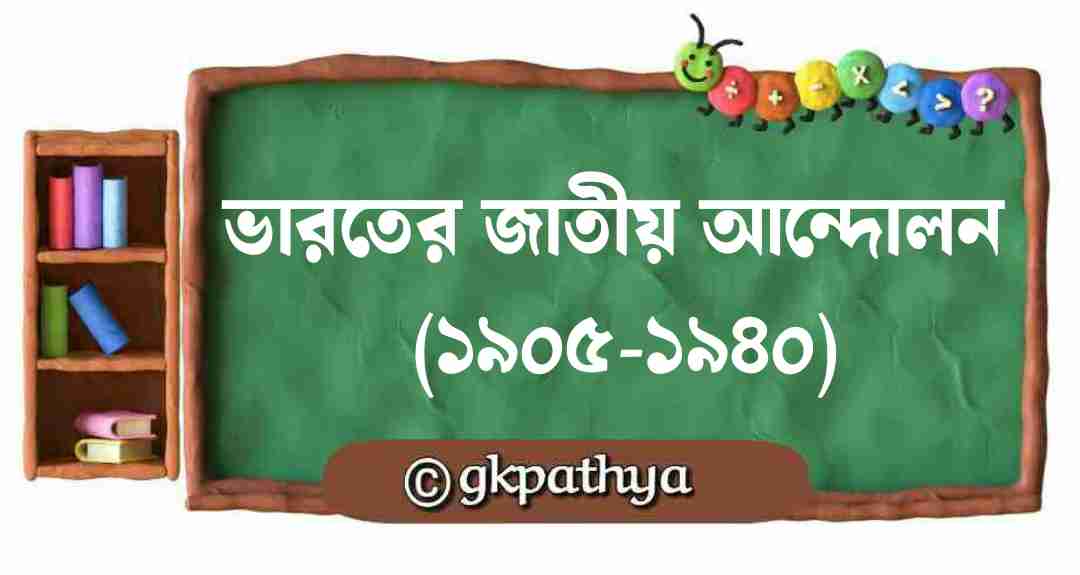
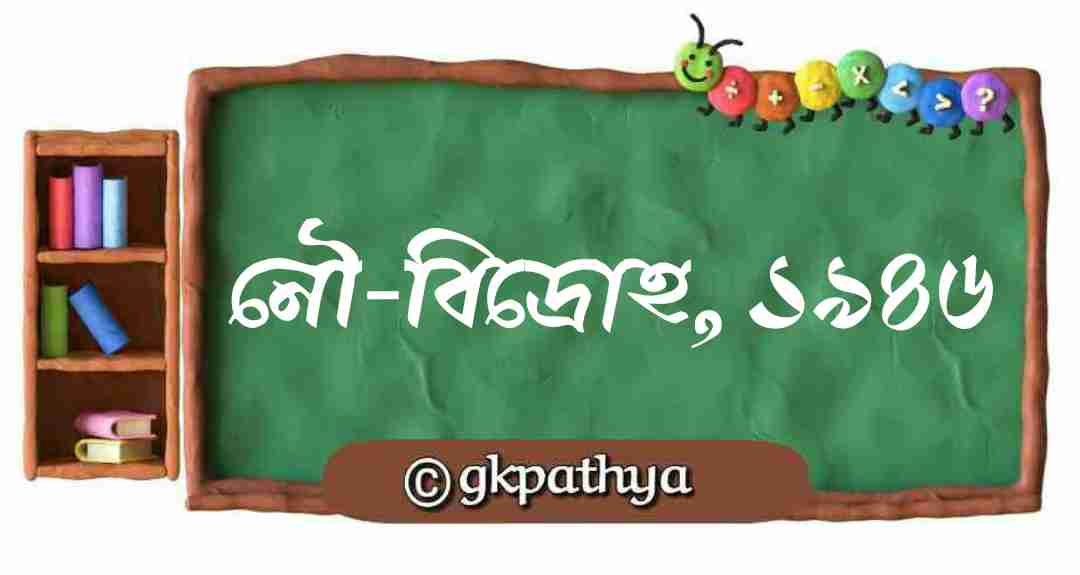

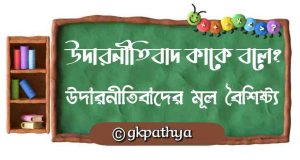
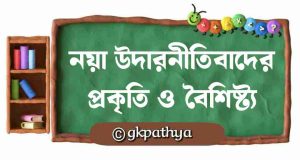

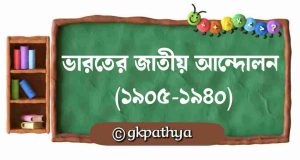
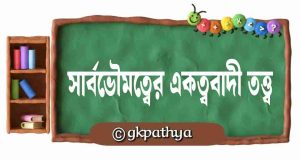
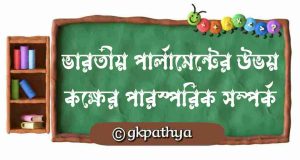
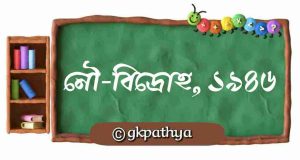


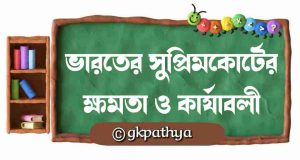
Post Comment