গণতন্ত্র: গণতন্ত্রের বিভিন্ন রূপ ও বৈশিষ্ট্য: Democracy: Different forms and characteristics of democracy.
গণতন্ত্র বলতে কী বোঝ?
রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা বিভিন্নভাবে গণতন্ত্রের অর্থের ব্যাখ্যা করেছেন। গণতন্ত্র শব্দটি এসেছে গ্রিক শব্দ
Demos এবং Kratos থেকে। Demos-এর অর্থ জনগণ (People) এবং Kratos-র অর্থ কর্তৃত্ব বা শাসন বা ক্ষমতা (Power or Authority)। অতএব Democracy বা গণতন্ত্রের অর্থ হল জনগণের শাসন বা জনগণের কর্তৃত্ব।
ব্যুৎপত্তিগত অর্থে গণতন্ত্র বলতে জনগণের শাসনকে বোঝানো হয়। তবে তত্ত্বগত পর্যালোচনায় গণতন্ত্র শব্দটিকে ব্যাপক ও সংকীর্ণ এই দুই অর্থে ব্যবহার করা হয়।
ব্যাপক অর্থে গণতন্ত্র বলতে কী বোঝ?
ব্যাপক অর্থে গণতন্ত্র বলতে এমন একটি শাসনব্যবস্থাকে বোঝানো হয় যেখানে সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সাম্য ও সমানাধিকার প্রতিষ্ঠিত থাকে। এইরূপ শাসনব্যবস্থায় নারী-পুরুষ, ধনী-দরিদ্র, জ্ঞানী-মূর্খ সকলেই সমান অধিকার লাভ করতে পারে। এখানে যে-কোনো ধরনের বৈষম্যমূলক আচরণকে অস্বীকার করা হয়। সি ডি বার্নসের মতে, একটি আদর্শ হিসেবে গণতন্ত্র হল এমন একটি সমাজব্যবস্থা, যেখানে প্রতিটি মানুষ সামাজিক দিক থেকে ভিন্ন পর্যায়ভুক্ত হলেও এক অর্থে তারা অভিন্ন সামাজিক মর্যাদার অধিকারী। অর্থাৎ সমাজের সকল নাগরিকই অবিচ্ছেদ্য ও অপরিহার্য অঙ্গ।
সংকীর্ণ অর্থে গণতন্ত্র বলতে কী বোঝ?
সংকীর্ণ অর্থে গণতন্ত্র বলতে গণতান্ত্রিক সরকার বা শাসনব্যবস্থাকে বোঝায়। এই ধরনের শাসনব্যবস্থায় জনসাধারণ প্রত্যক্ষভাবে কিংবা নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের মাধ্যমে পরোক্ষভাবে শাসনকার্যে অংশগ্রহণ করে। তাই সংকীর্ণ গণতন্ত্র বলতে অনেকেই জনগণের শাসনকে বুঝিয়েছেন। অধ্যাপক ডাইসির ভাষায় বলা যায়, যে শাসনব্যবস্থায় তুলনামূলকভাবে জনগণের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশের হাতে শাসনক্ষমতা ন্যস্ত থাকে, তাকে গণতন্ত্র (Democracy) বলে অভিহিত করা যায়। এককথায় সংকীর্ণ অর্থে গণতন্ত্র বলতে রাষ্ট্রপরিচালনার এক বিশেষ পদ্ধতিকে বোঝায়। এইরূপ ব্যবস্থায় সমাজের সকল ব্যক্তির কাছে রাজনৈতিক সাম্যের দাবি উন্মুক্ত থাকে, অর্থাৎ গণতন্ত্র হল রাষ্ট্রপরিচালনার এক বিশেষ পদ্ধতি।
গণতন্ত্রের সংজ্ঞা:
বিভিন্ন রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে গণতন্ত্রের সংজ্ঞা প্রদান করেছেন। যথা-
- জন স্টুয়ার্ট মিল: জন স্টুয়ার্ট মিল গণতন্ত্র বলতে রাষ্ট্রে সার্বভৌম ক্ষমতা প্রয়োগে সকলের সমানাধিকারের স্বীকৃতিকে বুঝিয়েছেন।
- ডাইসি: ডাইসি বলেন, গণতন্ত্র তাকেই বলা যায়, যেখানে দেশের সরকার পরিচালনায় অধিকাংশ মানুষ যোগদান করে।
- সিলি: সিলির মতে, যে শাসনব্যবস্থায় সকলের অংশগ্রহণের সুযোগ থাকে তা-ই গণতন্ত্র।
- ব্রাইস: ব্রাইস মনে করেন, যে শাসনব্যবস্থায় শাসন করার ক্ষমতা সমগ্র সমাজের হাতে ন্যস্ত থাকে, তাকেই গণতন্ত্র বলা যায়। তিনি বাস্তবে সংখ্যাগরিষ্ঠের শাসনকেই গণতন্ত্র বলে অভিহিত করেছেন।
- সিডি বার্নস: সি ডি বার্নস মনে করেন যে, গণতন্ত্র একই ধরনের মানুষ নিয়ে গঠিত নয়। তাঁর মতে, প্রত্যেকেই সমাজের অবিচ্ছেদ্য ও অপরিহার্য অংশ। এদিক থেকে তারা সকলেই সমান। অতএব সমমর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তিদের নিয়ে গঠিত সমাজই হল গণতন্ত্র।
- রুশো: রুশোর মতে, সাধারণ ইচ্ছার দ্বারা পরিচালিত সরকারই হল গণতন্ত্র।
গণতন্ত্রের বিভিন্ন রূপ:
অধ্যাপক গার্নার সরকার গঠনের উপর ভিত্তি করে গণতন্ত্রকে দু-ভাগে ভাগ করেছেন, যথা-
প্রত্যক্ষ গণতন্ত্র বলতে কী বোঝ?
গণতন্ত্রের রূপগুলির মধ্যে আদি রূপ বা প্রাচীন রূপ হল প্রত্যক্ষ গণতন্ত্র। যে শাসনব্যবস্থায় রাষ্ট্রের সমস্ত নাগরিকরা প্রত্যক্ষভাবে মিলিত হয়ে দেশের শাসনকার্য পরিচালনা করে, তাকে প্রত্যক্ষ গণতন্ত্র (Direct Democacy) বলা হয়। বর্তমানে সুইটজারল্যান্ডের চারটি ক্যান্টন এবং অর্ধক্যান্টনে ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কয়েকটি স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনমূলক প্রতিষ্ঠানের মধ্যে এইরূপ গণতন্ত্র দেখতে পাওয়া যায়। এই ধরনের শাসনব্যবস্থাকে অংশগ্রহণকারী গণতন্ত্র বা Participatory Democracy-ও বলা হয়।
পরোক্ষ গণতন্ত্র বলতে কী বোঝ?
রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় সবচেয়ে উৎকৃষ্ট ব্যবস্থা হল গণতন্ত্র। এই গণতন্ত্রেরই অন্যতম রূপ হল পরোক্ষ গণতন্ত্র। পরোক্ষ গণতন্ত্র হল এমন একটি শাসন যেখানে জনগণ প্রত্যক্ষভাবে শাসনকার্যে অংশগ্রহণ করে না। জনগণ নির্দিষ্ট সময়ের জন্য কিছু ব্যক্তিকে নির্বাচিত করে। এই জনপ্রতিনিধিরাই দেশ শাসন করে। তাই পরোক্ষ গণতন্ত্রকে প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্র (Representative Democracy) বলা হয়।
পরোক্ষ গণতন্ত্র দেখতে পাওয়া যায়-গ্রেট ব্রিটেন, ফ্রান্স, অস্ট্রেলিয়া, কানাডা প্রভৃতি রাষ্ট্রে।
সরকার পরিচালনার দৃষ্টিকোণ থেকেও গণতন্ত্রকে দু-ভাগে ভাগ করা হয়, যথা-
উদারনৈতিক বা বুর্জোয়া গণতন্ত্র বলতে কী বোঝ?
উনিশ শতকে উদারনীতিবাদ এবং গণতন্ত্র -এই দুটি ধারণার সংযুক্তিকরণের মাধ্যমে উদারনৈতিক গণতন্ত্রের (Bourgeois Democracy) উদ্ভব ঘটে। উদারনৈতিক গণতন্ত্র গ্রেট ব্রিটেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রভৃতি দেশে দেখতে পাওয়া যায়।
সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্র বলতে কী বোঝ?
সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় উৎপাদন ব্যবস্থার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্র (Socialist Democracy) গড়ে ওঠে। সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রকে সমাজতন্ত্র বা সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য হিসেবে গণ্য করা হয়। সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্র গণপ্রজাতন্ত্রী চিন, কিউবায় দেখতে পাওয়া যায়।
গণতন্ত্রের বৈশিষ্ট্যসমূহ:
গণতন্ত্রের বেশ কয়েকটি মৌলিক বৈশিষ্ট্য রয়েছে, যা রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় নাগরিকদের অংশগ্রহণ এবং অধিকারের সুরক্ষা নিশ্চিত করে। বৈশিষ্ট্যগুলি হল-
গণসার্বভৌমত্ব:
গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় সরকারি কর্তৃপক্ষ জনগণের সম্মতির ভিত্তিতে গড়ে ওঠে এবং টিকে থাকে। নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মাধ্যমে জনগণ তাদের এই ক্ষমতা প্রয়োগ করে থাকে।
আইনের অনুশাসন:
গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় সকল ব্যক্তি এবং সমাজস্থ সকল ধরনের প্রতিষ্ঠানসমূহ রাষ্ট্রীয় আইনের প্রতি অনুগত থাকে। যে-কোনো ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানকে আইনের প্রতি দায়বন্ধশীল থেকে নিজ নিজ কার্যসম্পাদন করতে হয়, অন্যথায় এই আইন বাস্তবে সকলের উপর সমভাবে প্রযুক্ত হয়। একেই আইনের অনুশাসন (Rule of Law) বলা হয়।
রাজনৈতিক সাম্য:
গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা মূলত রাজনৈতিক সাম্যের উপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত। রাজনৈতিক সাম্য বলতে, রাজনীতি তথা রাষ্ট্রনীতিতে সকলের অংশগ্রহণের সমান সুযোগসুবিধাকে বোঝায়। প্রার্থী নির্বাচনে অংশগ্রহণ বা ভোটদানের অধিকার, নির্বাচিত হওয়ার অধিকার বা নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার অধিকার ইত্যাদি ক্ষেত্রে সমান সুবিধা ভোগ করাকেই রাজনৈতিক সাম্য বলে মনে করা হয়। এখানে রাজনৈতিক অংশগ্রহণে জন্মগত বা ধনগত বৈষম্যকে স্বীকার করা হয় না, সকলেই সমমর্যাদা ও সমানাধিকারসম্পন্ন।
সংখ্যাগরিষ্ঠের শাসন ও সংখ্যালঘু অধিকার সংরক্ষণ:
গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় সংখ্যাগরিষ্ঠের সিদ্ধান্তকে অধিক গুরুত্ব দেওয়ার ফলে এই ধরনের শাসনব্যবস্থা সংখ্যাগরিষ্ঠের শাসনে পরিণত হয়। রাজনৈতিক ভোটাভুটিতে যে দল সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে, সেই দলের নেতা বা নেত্রী সরকার গঠন ও পরিচালনা করার সুযোগ পান। অনেকে তাই মনে করেন, গণতন্ত্র কখনোই সমাজের সমগ্র অংশের শাসন নয়, কেবলমাত্র সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশেরই শাসনমাত্র।
অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন:
গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল, অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন (Free and Fair Election)। এখানে নির্বাচন প্রক্রিয়াটি নিরপেক্ষভাবে পরিচালিত হয়, যাতে রাষ্ট্রের সকল যোগ্য নাগরিক যে-কোনো দলের প্রার্থী কিংবা যে-কোনো দলের সদস্যপদ গ্রহণের সমান সুযোগ ভোগ করতে পারে।
প্রতিনিধিত্বমূলক সরকার:
গণতন্ত্র বলতে বর্তমানে প্রতিনিধিত্বমূলক গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকেই বোঝায়। বিশ্বের প্রায় অধিকাংশ রাষ্ট্রই বর্তমানে আয়তন ও জনসংখ্যার দিক থেকে বৃহৎ। ফলত, জনসাধারণের পক্ষে প্রত্যক্ষভাবে বা সরাসরি শাসনকার্যে অংশগ্রহণ করা সম্ভব নয়। তাই আধুনিককালে পরোক্ষ বা প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্র (Indirect or Representative Democracy) প্রাধান্য পেয়েছে।
প্রতিনিধি নির্বাচন:
এই শাসনব্যবস্থায় জনগণ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই প্রত্যক্ষভাবে শাসনকার্য পরিচালনা করে না। নির্দিষ্ট সময় অন্তর জনগণ সর্বজনীন প্রাপ্তবয়স্ক ভোটাধিকারের ভিত্তিতে নির্বাচনের মাধ্যমে নিজেদের প্রতিনিধিদের দ্বারা শাসনকার্যে অংশগ্রহণ করে। জনপ্রতিনিধিরাই শাসনক্রিয়াকে সচল রাখতে সাহায্য করে।
গণঅংশগ্রহণ:
গণতন্ত্রে নাগরিকরা কখনও সরাসরি আবার কখনও বা নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মাধ্যমে রাষ্ট্রের বিভিন্ন বিষয় সিদ্ধান্তগ্রহণ প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করে থাকে।
ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতির উপস্থিতি:
গণতন্ত্রে ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতির (Separation of Powers) উপস্থিতি লক্ষ করা যায়। অর্থাৎ, সরকারের তিনটি বিভাগ যথা-শাসন বিভাগ, আইন বিভাগ ও বিচার বিভাগ সম্পূর্ণ স্বতন্ত্রভাবে তাদের কার্যসম্পাদন করে। কিন্তু সরকারের কোনো একটি বিভাগ যাতে স্বৈরাচারী হয়ে না ওঠে বা ক্ষমতা কুক্ষিগত করে না ফেলতে পারে, সেক্ষেত্রে বর্তমানে নিয়ন্ত্রণ ও ভারসাম্যের নীতি (Checks and Balance)-টিও প্রাধান্য পেয়েছে।
বহুত্ববাদ:
আধুনিক গণতন্ত্রের অপর একটি বৈশিষ্ট্য হল বহুত্ববাদ (Pluralism)-এর স্বীকৃতি। বর্তমানে রাজনৈতিক মতামতের বৈচিত্র্যময়তা, বহুবিধ রাজনৈতিক দলের উপস্থিতি, স্বার্থগোষ্ঠীসমূহের অস্তিত্বকে গণতন্ত্রে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে এবং তাদের সহাবস্থানকে উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে।
দায়বদ্ধতা ও স্বচ্ছতা:
গণতন্ত্রে সরকার জনগণের কাছে দায়বদ্ধ থাকে। সরকারি কার্যাবলির উপর জনগণের বিশ্বাস সুনিশ্চিত করতে এবং দুর্নীতি প্রতিরোধ করার উদ্যোগ গ্রহণ করতেই সরকারকে জনসাধারণের নিকট জবাবদিহি করতে হয়। ফলে সরকারি কার্যের স্বচ্ছতা বৃদ্ধি পায়।
জনসম্মতিতে এবং জনস্বার্থে পরিচালিত:
গণতন্ত্রে সরকার পরিচালনার দায়িত্ব সংখ্যাগরিষ্ঠ শ্রেণির হাতে ন্যস্ত থাকে। কিন্তু, এই শাসনকার্য কেবলমাত্র সংখ্যাগরিষ্ঠের স্বার্থেই নয়, জনগণের সার্বিক কল্যাণের জন্যও পরিচালিত হয়। এই শাসনব্যবস্থায় সংখ্যালঘু স্বার্থ সংরক্ষণ ও তাদের মতামতকেও স্বীকৃতি প্রদান করা হয়, তাই রাষ্ট্রের সংখ্যালঘু অংশও গণতন্ত্রকে সমর্থন করে। অর্থাৎ, রাষ্ট্রের সমগ্র অংশই গণতন্ত্রকে সমর্থন করে। এই কারণেই গণতন্ত্রকে জনসম্মতির উপর প্রতিষ্ঠিত সরকার (Government based on Consent) বলে অভিহিত করা হয়।
জনমতের গুরুত্ব:
গণতন্ত্র যেহেতু জনমতের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত, তাই অনেকে জনমতকে গণতন্ত্রের প্রাণ বলার পক্ষপাতী। জনমতকে উপেক্ষা করে গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা পরিচালিত হতে পারে না। তাই সকল সরকারি সিদ্ধান্ত জনমতের ভিত্তিতে গৃহীত হয়।
মানবাধিকারের সংরক্ষণ:
গণতন্ত্রের একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল মানবাধিকারের সংরক্ষণ। গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় মৌলিক অধিকার ও স্বাধীনতা, বাক্ ও মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা, আইনসভায় মতামত প্রকাশের অধিকার, ধর্মীয় স্বাধীনতা প্রভৃতির মাধ্যমে রাষ্ট্র নাগরিকদের মানবাধিকার সংরক্ষিত রাখার প্রচেষ্টা করে।
প্রত্যক্ষ গণতন্ত্রের গুণ বা সুবিধা:
জনগণই শক্তির প্রয়োগ ও ব্যবহারের অধিকারী:
প্রত্যক্ষ গণতন্ত্রের সর্বপ্রধান সুবিধা হল, এই ব্যবস্থায় তত্ত্বগতভাবে সার্বভৌম শক্তির অধিকারী জনসাধারণ বাস্তবে ওই শক্তির প্রয়োগ ও ব্যবহারের অধিকারী। এই ব্যবস্থাকে বিশুদ্ধ গণতন্ত্রও বলা যায়, তার কারণ জনসাধারণের ইচ্ছা ও মতামতের ভিত্তিতেই সমগ্র শাসনব্যবস্থা পরিচালিত হয়।
প্রত্যক্ষ গণতন্ত্র সহজ ও সরল:
প্রত্যক্ষ গণতান্ত্রিক শাসন সহজ ও সরল এবং কম ব্যয়বহুল। এইরূপ গণতন্ত্রে জনগণ আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। এই গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা সহজ, সরল প্রকৃতির হওয়ায় আইন, শাসন এবং বিচার বিভাগের মধ্যে কোনো পার্থক্য দেখতে পাওয়া যায় না।
নাগরিকদের রাজনৈতিক সচেতনতা বৃদ্ধি:
প্রত্যক্ষ গণতন্ত্রে সমস্ত প্রাপ্ত বয়স্ক নাগরিকরা শাসনকার্যে অংশগ্রহণ করে। এর ফলে সে দেশের সমস্যা সম্বন্ধে অবহিত হয় এবং সমাধানের ব্যাপারে একে অপরের সঙ্গে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে সিদ্ধান্ত গ্রহণে অংশ নেয়। তাই নাগরিকদের শিক্ষা ও রাজনৈতিক চেতনা বৃদ্ধি পায়।
দ্রুত সিদ্ধান্তগ্রহণ:
প্রত্যক্ষ গণতন্ত্রে শাসক ও শাসিতের সরাসরি সম্পর্ক থাকার ফলে যে-কোনো বিষয়ে দ্রুত সিদ্ধান্তগ্রহণ করা সম্ভব হয়। এর ফলে আলোচ্য বিষয়টিকে অন্য কোনো স্থানে প্রেরণ করতে হয় না। ফলে এইরূপ গণতন্ত্রকে অনেকে জরুরি অবস্থার উপযোগী বলে মনে করেন।
সরকারের স্বৈরাচারিতা রোধ:
প্রত্যক্ষ গণতন্ত্রে রাষ্ট্রীয় প্রশাসনের সকল স্তরে জনগণের সক্রিয় অংশগ্রহণ থাকে বলে, সরকার জনদরদি ও জনকল্যাণকামী ভূমিকা পালন করে থাকে। এর ফলে সরকারের স্বৈরাচারিতা জনগণের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়।
ব্যয়সাপেক্ষ:
এরূপ শাসনব্যবস্থা প্রতিনিধিত্বমূলক গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার ন্যায় ব্যয়বহুল নয়।
আইন প্রণয়ন পদ্ধতি:
প্রত্যক্ষ গণতন্ত্রে আইন প্রণয়ন পদ্ধতিটি অত্যন্ত সহজ ও সরল প্রকৃতির হয়ে থাকে। এরূপ গণতন্ত্রে জনগণ নির্দিষ্ট একটি স্থানে সমবেত হয়ে আইন প্রণয়নের ব্যবস্থা গ্রহণ করে থাকে। ফলে সময়ের অপচয়ও ঘটে না।
জনগণ দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়:
প্রত্যক্ষ গণতন্ত্রে জনগণকে প্রশাসনিক কার্য ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের বিষয়ে সুযোগ দেওয়ার ফলে তারা নিজেদেরকে রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ অংশ বলে মনে করে। জনগণ নিজেদের সম্মান ও মর্যাদার ব্যাপারে সচেতন হয়। এর ফলে গভীর দেশপ্রেম ও জাতীয়তাবাদ জন্ম নেয়।
আমলাতন্ত্রের প্রভাবমুক্ত:
প্রত্যক্ষ গণতন্ত্র আমলাতান্ত্রিক প্রভাব থেকে মুক্ত। কারণ এই শাসনব্যবস্থায় জনগণের দ্বারা নির্বাচিত কোনো প্রতিনিধিরা তাদের আমলা বা উচ্চপদস্থ কর্মচারী দ্বারা শাসনকার্য সম্পন্ন করে না। এর ফলে জনগণ সরাসরি প্রশাসনিক কাজে হস্তক্ষেপ করে।
বিপ্লবের আশঙ্কামুক্ত:
এইরূপ গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় জনগণ ব্যাপকভাবে অংশগ্রহণ করায় তাদের মধ্যে কোনো দীর্ঘকালীন অসন্তোষ দানা বাঁধতে পারে না, ফলে বিপ্লবের আশঙ্কা এখানে থাকে না।
মূল্যায়ন:
পরিশেষে বলা যায়, বর্তমান বিশ্বে প্রত্যক্ষ গণতন্ত্র একেবারে অচল, তবুও আধুনিক গণতন্ত্রের আদিরূপ হিসেবে প্রত্যক্ষ গণতন্ত্রের ভূমিকাকে অস্বীকার করা যায় না।
প্রত্যক্ষ গণতন্ত্রের দোষ বা অসুবিধা:
প্রত্যক্ষ গণতন্ত্রের কিছু সুবিধা থাকলেও এই শাসনব্যবস্থা পুরোপুরি ত্রুটিমুক্ত নয়। প্রত্যক্ষ গণতন্ত্রের দোষ বা অসুবিধাগুলি হল-
অকার্যকর শাসনব্যবস্থা:
বর্তমানে বিশ্বের প্রায় অধিকাংশ রাষ্ট্র বৃহদায়তন ও বিপুল জনসংখ্যাবিশিষ্ট। আর এরূপ শাসনব্যবস্থার সবচেয়ে বড়ো ত্রুটি হল বৃহদায়তন রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে এই ব্যবস্থা শুধুমাত্র অকার্যকরই নয়, অকাম্যও বটে। কারণ, একটি বৃহৎ রাষ্ট্রের সকল জনগণ দেশের নানান প্রান্ত থেকে এসে একত্রিতভাবে আইন প্রণয়ন করবে- এই ধারণা নিছকই একটি কল্পনামাত্র।
আইন প্রণয়ন ও নীতি নির্ধারণ অসম্ভব:
প্রত্যক্ষ গণতন্ত্রে দেশের সকল যোগ্য নাগরিকগণ মতামত প্রকাশের সমসুযোগ পায়। এর ফলে কোনো বিশেষ পরিস্থিতিতে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আইন প্রণয়ন বা নীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে নানান সমস্যা সৃষ্টির সম্ভবনা থাকে। কারণ এমতাবস্থায় সকলেই নিজেদের অভিমত প্রকাশ করতে আগ্রহী হয়ে পড়ে। ফলে, পরস্পরবিরোধী নানান মতামতগুলির মধ্যে সমন্বয়সাধন করে নীতি নির্ধারণ ও আইন প্রণয়ন অসম্ভব হয়ে পড়ে।
অগণতান্ত্রিক নীতি নির্ধারণ:
অনেকে মনে করেন, রাষ্ট্রপরিচালনার ন্যায় জটিল ও গুরুত্বপূর্ণ কার্যসম্পাদনের জন্য যে রাজনৈতিক জ্ঞান, বিচক্ষণতা ও দূরদৃষ্টিতা থাকা বাঞ্ছনীয়, তা রাষ্ট্রের সকল নাগরিকদের মধ্যে থাকা সম্ভব নয়। ফলে এই ধরনের শাসনব্যবস্থায় জনস্বার্থবিরোধী কার্যাবলি সম্পাদন অগণতান্ত্রিক নীতি প্রণয়ন ইত্যাদি হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।
স্বৈরতন্ত্রের উন্মেষ:
এই ধরনের শাসনব্যবস্থায় যদি নাগরিকদের রাষ্ট্রীয় কার্যকলাপে ঔদাসীন্যতা দেখা দেয়, তাহলে মুষ্টিমেয় কিছু ব্যক্তির হাতে শাসনক্ষমতা কেন্দ্রীভূত হওয়ার সম্ভবনা পরিলক্ষিত হয়। ফলস্বরূপ গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা স্বৈরতন্ত্রে রূপান্তরিত হয়।
সাংস্কৃতিক বিকাশের পরিপন্থী:
প্রত্যক্ষ গণতন্ত্রকে সাংস্কৃতিক বিকাশের পরিপত্রী বলে মনে করা হয়। রাষ্ট্রের সকল জনসাধারণই যদি শাসনকার্যে অংশগ্রহণ করে, তাহলে শিল্প, সাহিত্য, চারুকলা, সংগীত প্রভৃতি দিকগুলি ক্রমাগত অবহেলিত হতে থাকবে। এতে দেশের সর্বাঙ্গীণ বিকাশ ব্যাহত হবে।
আপতকালীন পরিস্থিতির পক্ষে অনুপোযোগী:
প্রত্যক্ষ গণতন্ত্র আপতকালীন পরিস্থিতির ক্ষেত্রে উপযোগী নয় বলে অনেকে অভিমত পোষণ করেছেন। বহিঃশক্তির আক্রমণ বা আভ্যন্তরীণ যুদ্ধবিগ্রহের পরিস্থিতিতে যদি দ্রুত সিন্ধান্তগ্রহণের প্রয়োজন হয়, তখন জনগণের ইচ্ছা-অনিচ্ছার উপর ভিত্তি করে ক্রমাগত কালবিলম্ব হয়।
বৈচিত্র্যপূর্ণ ভাষা ও সংস্কৃতি:
বহু ভাষাভাষি ও বহু সংস্কৃতিসম্পন্ন জনগণের বৈচিত্র্যপূর্ণতা একই রাষ্ট্রে পরিলক্ষিত হলে, সেই রাষ্ট্রে প্রত্যক্ষ গণতন্ত্র সাফল্যমণ্ডিত হওয়ার সম্ভবনা একেবারেই থাকে না।
ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতির অনুপস্থিতি:
প্রত্যক্ষ গণতন্ত্রে ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতির বাস্তব প্রয়োগ কখনোই সম্ভব হয়ে ওঠে না। কারণ এখানে আইন, শাসন ও বিচার বিভাগের কার্যাবলির মধ্যে তেমন কোনো সুস্পষ্ট পার্থক্য পরিলক্ষিত হয় না। ফলে অনেক সময় রাষ্ট্রপরিচালনায় জটিলতারও সৃষ্টি হয়।
শাসনতান্ত্রিক বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি:
প্রত্যক্ষ গণতন্ত্রে শাসনতান্ত্রিক বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয় বলে সমালোচনা করা হয়। কারণ, যখনই সাধারণ মানুষ সরকারি কার্যাবলিতে প্রত্যক্ষভাবে অংশ নেয়, তখনই তারা পরস্পর পরস্পরের চেয়ে কোনো অংশে কম নয়-এই ধারণার বশবর্তী হয়ে সিদ্ধান্তগ্রহণ করতে যায় এবং যার ফল বিপথগামী হয়। তবে একথা সত্য যে, সুষ্ঠুভাবে শাসনকার্য পরিচালনার জন্য দেশের প্রতি যে মমত্ববোধ, কর্তব্যপরায়ণতা, সুশিক্ষিত বিচারবোধ, দেশপ্রেম প্রয়োজন তা কখনোই সকলের মধ্যে উপস্থিত থাকে না। ফলে এরূপ গণতন্ত্র বাস্তবে ব্যর্থ হয়।
অনুপযুক্ত শাসনব্যবস্থা:
বর্তমানে আধুনিক জনকল্যাণকামী রাষ্ট্রের বহুমুখী কার্যকলাপের পরিপ্রেক্ষিতে প্রত্যক্ষ গণতন্ত্র কখনোই উপযুক্ত গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা নয়।
জনগণের আবেগ দ্বারা পরিচালিত শাসনব্যবস্থা:
সর্বোপরি বলা যায় যে, প্রত্যক্ষ গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে আইন ও শাসনকার্য পরিচালনার ক্ষেত্রে জনগণ অনেকসময় উত্তেজনা বা ভাবাবেগের দ্বারা পরিচালিত হয়। এরূপ পরিস্থিতিতে আইন প্রণয়ন বা শাসনকার্য পরিচালনা করলে, দেশের কল্যাণের পরিবর্তে অকল্যাণ হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি থাকে।
মূল্যায়ন:
উপরোক্ত আলোচনায় প্রত্যক্ষ গণতন্ত্রের অসুবিধা বা ত্রুটিগুলি উল্লেখ করা হলেও প্রত্যক্ষ গণতন্ত্রের সাফল্য প্রমাণ করে দেয় যে, এই শাসনব্যবস্থা স্বৈরতন্ত্র ও একনায়কতন্ত্রের মধ্যযুগীয় একচ্ছত্র আধিপত্য থেকে জনগণকে মুক্তি দিয়ে স্বাধীনতার দ্বারলগ্নে পৌঁছে দিয়েছে।
পরোক্ষ গণতন্ত্রের সুবিধা ও অসুবিধা:
পরোক্ষ গণতন্ত্রের সুবিধা (Advantages of Indirect Democracy):
ব্যবহারিক ও কার্যকর ব্যবস্থা:
প্রত্যেক নাগরিকের সরাসরি সিদ্ধান্ত নেওয়া কঠিন। নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মাধ্যমে শাসন পরিচালনা করা সহজ ও বাস্তবসম্মত।
সময় ও অর্থের সাশ্রয়:
প্রত্যেক সিদ্ধান্তে জনগণের অংশগ্রহণ করলে প্রচুর সময় ও অর্থ ব্যয় হতো। পরোক্ষ গণতন্ত্রে এই খরচ অনেক কম হয়।
যোগ্য নেতৃত্বের সুযোগ:
নির্বাচিত প্রতিনিধিরা সাধারণত অভিজ্ঞ, শিক্ষিত ও যোগ্য হন, ফলে তারা রাষ্ট্র পরিচালনায় দক্ষতা দেখাতে পারেন।
স্থিতিশীল সরকার গঠনে সহায়ক:
প্রত্যক্ষ গণতন্ত্রের তুলনায় পরোক্ষ গণতন্ত্রে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা বেশি থাকে, কারণ সরকার নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য নির্বাচিত হয়।
বৃহৎ রাষ্ট্রে প্রযোজ্য:
জনসংখ্যা ও ভৌগোলিকভাবে বিশাল রাষ্ট্রে প্রত্যক্ষ গণতন্ত্র চালানো সম্ভব নয়। তাই পরোক্ষ গণতন্ত্রই সেখানে বাস্তবসম্মত।
জনমতের প্রতিফলন ঘটে:
প্রতিনিধিরা জনগণের ইচ্ছা ও চাহিদা অনুযায়ী সিদ্ধান্ত নেন, ফলে জনগণের মতামত পরোক্ষভাবে শাসনে প্রতিফলিত হয়।
পরোক্ষ গণতন্ত্রের অসুবিধা (Disadvantages of Indirect Democracy):
জনগণের ইচ্ছা থেকে বিচ্যুতি:
নির্বাচিত প্রতিনিধিরা প্রায়ই নিজেদের স্বার্থে কাজ করেন, ফলে জনগণের প্রকৃত ইচ্ছা প্রতিফলিত হয় না।
দুর্নীতি ও ক্ষমতার অপব্যবহার:
রাজনৈতিক দল ও নেতারা ক্ষমতা ধরে রাখতে দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতি ও অনৈতিক উপায়ে কাজ করতে পারেন।
দলীয় রাজনীতির প্রভাব:
দলীয় স্বার্থ ও রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা প্রায়ই জাতীয় স্বার্থের উপরে চলে যায়।
জনগণের উদাসীনতা:
জনগণ ভোট দেওয়ার পর রাজনৈতিক বিষয়ে আগ্রহ হারায়, ফলে গণতন্ত্রের প্রাণশক্তি কমে যায়।
অযোগ্য প্রতিনিধির নির্বাচন:
অনেক সময় ভোটাররা আবেগে বা ভুল তথ্যের ভিত্তিতে অযোগ্য ব্যক্তিকে ভোট দেন, যা শাসন ব্যবস্থাকে দুর্বল করে।
ধনীদের প্রভাব বৃদ্ধি:
নির্বাচনী প্রক্রিয়ায় টাকা ও ক্ষমতার প্রভাব থাকে, ফলে ধনী ও প্রভাবশালীরাই রাজনীতিতে প্রাধান্য পান।
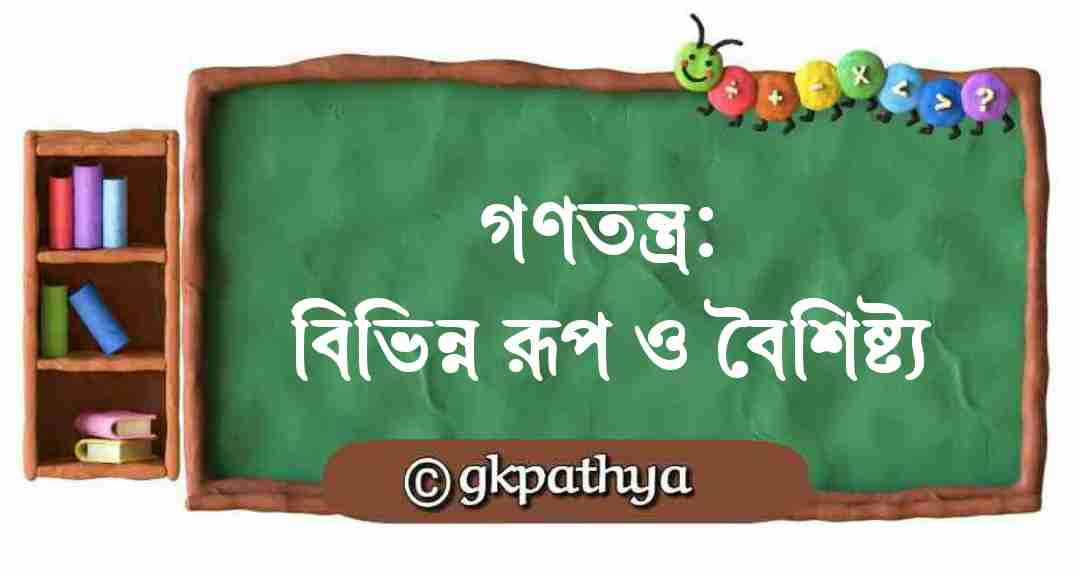
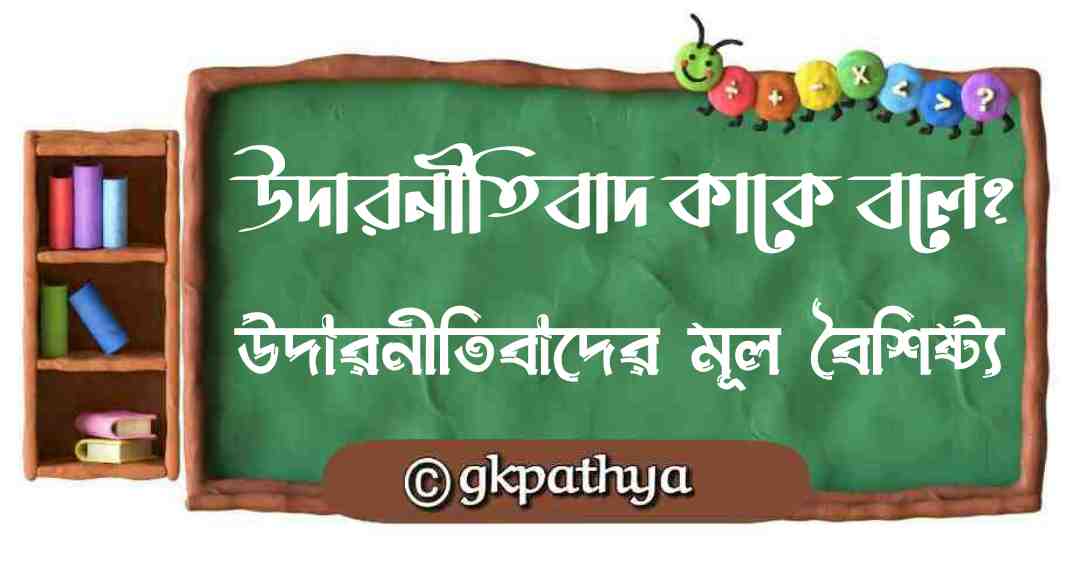
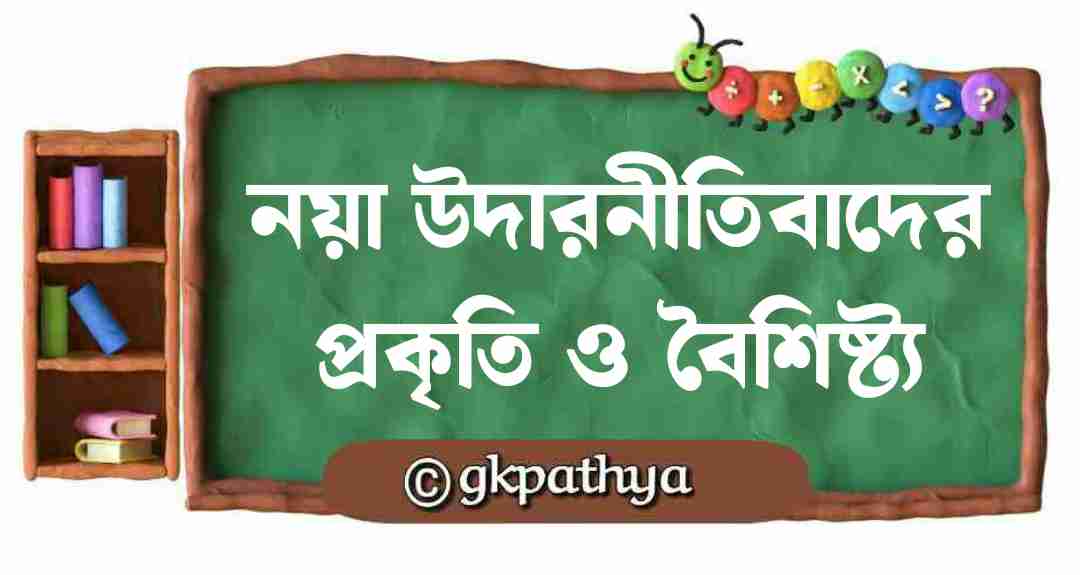

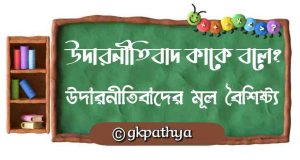
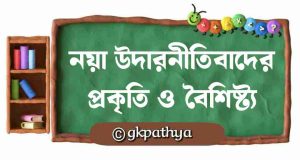

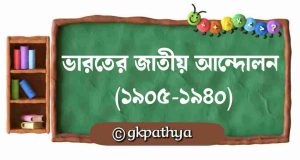
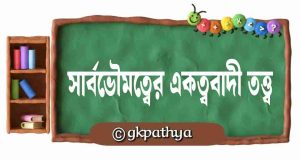
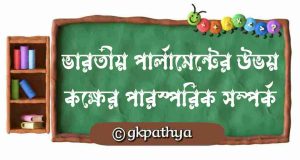
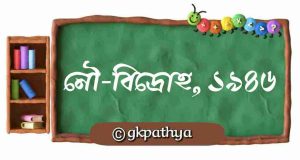


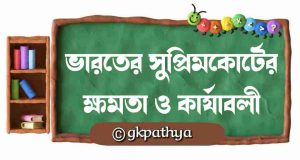
Post Comment