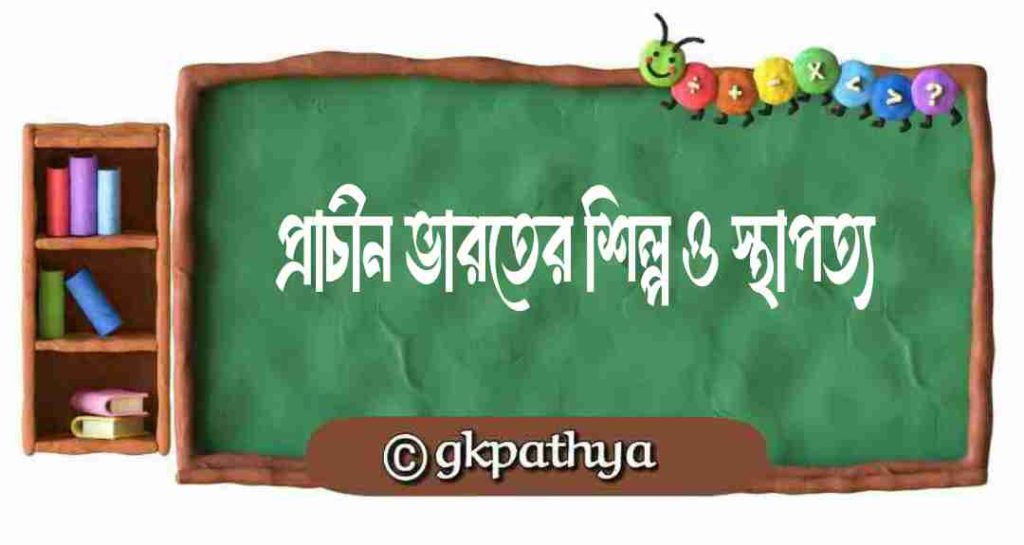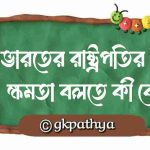মৌর্যযুগে ভারতীয় শিল্পকলার নতুন যাত্রা শুরু হয়। অধ্যাপক শাস্ত্রী ও ড. বাগচি তাই মৌর্য শিল্পকলা সম্পর্কে বলেছেন, ‘স্থাপত্যশিল্পের ক্ষেত্রে মৌর্যযুগ একটি লক্ষণীয় অধ্যায়ের সূচনা করেছে।‘ চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের আমলে আগত মেগাথিনিস ও দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের আমলে আগত ফা-হিয়েনের বিবরণীতে মৌর্য শিল্পকলার উচ্চ প্রশংসা করা হয়েছে।
ফা-হিয়েন মন্তব্য করেছিলেন, ‘এ মানুষের সৃষ্টি হতে পারে না, হয় দেবতার, না হলে কোনাে দানবের তৈরি।‘ মেগাস্থিনিস চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের রাজপ্রাসাদের পালিশ করা কাঠের কাজ দেখে অবাক হয়েছিলেন। সম্রাট অশােকের আমলে ৮৪,০০০ বৌদ্ধস্তৃপ, অসংখ্য স্তম্ভ, বৌদ্ধ ও আজীবক সন্ন্যাসীদের তৈরি গুহা, চৈত্য, প্রাসাদ প্রভৃতির স্থাপত্য ভাস্কর্য, কারুকার্য এককথায় অনুপম। সাঁচি, সারনাথ, এলাহাবাদ, নন্দনগড়, রুম্মিনদেই প্রভৃতি স্থানে বহু কারুকার্যময় বৌদ্ধস্তুপ বা স্তম্ভ পাওয়া গেছে।
মৌর্য শিল্প রীতি:
সারনাথের অশােকস্তম্ভের শীর্ষদেশে ‘সিংহের মুর্তি’ ও ‘অশােকচক্র চিত্র’ আজও বিস্ময়ের উদ্রেক কুরে। এছাড়া বেসনগরের গরুড় স্তম্ভ ও ভারতের স্তম্ভ এবং পাটলিপুত্র দুর্গের প্রাচীরের চারদিকে কারুকার্যময় ৬৪টি সিংহদুয়ার, ৫৭০টি তােরণ মৌর্য শিল্পের সমৃদ্ধির এক জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত। বিভিন্ন গুহার মধ্যে নাগার্জুন – গুহা, দশরথ গুহা, সুদাম গুহার দেয়ালগুলি ঝকঝকে আয়নার মতাে মসৃণ ছিল।
স্তম্ভগুলির সবচেয়ে বডােটির উচ্চতা প্রায় ৫০ ফুট। বহু স্তম্ভের শীর্ষে পাথরের সিংহ, অশ্ব, হস্তী, বৃষ প্রভৃতি জীবজন্তুর মূর্তি খােদাই করা ছিল। পাটনার সন্নিকটে কুমারহারে ৮০টি স্তম্ভযুক্ত একটি হলঘর পাওয়া গেছে। লােরিয়া অশােকস্তম্ভ নন্দনগড় ও ওড়িশার ধৌলী পাহাড়ের হস্তীমুর্তিটি স্থাপত্যশিল্পের এক বিরল দৃষ্টান্ত সন্দেহ নেই। লােরিয়া নন্দনগড়ের স্তম্ভে আহাররত এক সুন্দর রাজহংসের মূর্তি আছে। এই স্তম্ভটি ৩২ ফুট আড়াই ইঞ্চি উঁচু এবং নীচের থেকে উপরে ব্যাস সাড়ে ৩৫ – সাড়ে -২৭ ইঞ্চি। সারনাথের স্তম্ভটি ৭ ফুট উঁচু। এই সিংহস্তম্ভটি বর্তমানে আমাদের রাষ্ট্রীয় প্রতীক হিসাবে গৃহীত হয়েছে। ড. ডি. ডি. কোশাম্বী মৌর্য শিল্পকলার প্রশংসা করে একইভাবে লিখেছেন, “সিন্ধুর পত্যের চেয়েও সুন্দর শিল্পস্থাপত্য অশােকের সময় থেকে শুরু হয়”।
গান্ধর শিল্প রীতি:
ভারতের শিল্প-স্থাপত্যের ইতিহাসে খ্রিঃ পূঃ ৫০ থেকে ৫০০ খ্রিঃ পর্যন্ত এক বিশেষ গল্পরীতির বিকাশ ঘটে। ভারতের উত্তর-পশ্চিমে গান্ধার রাজ্যে গ্রিক, রোমান ও ভারতীয় শিল্পরীতির সংমিশ্রণে এই শিল্পের উৎপত্তি ঘটে। রাজ্যের নাম অনুসারে এই শিল্পের নামকরণ হয় ‘গান্ধর শিল্প’ (Gandhara art)।
এই শিল্পের প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি হল—
- রােমান, গ্রিক ও ভারতীয় শিল্পরীতির সমন্বয়ে এই শিল্প গঠিত।
- চুন, বালি, পাথর, পােড়ামাটি, মাটি ও প্লাস্টার অফ প্যারিস দিয়ে মূর্তি নির্মাণের প্রবর্তন।
- গরুড়, যক্ষ ও বুদ্ধমূর্তি নির্মাণে গ্রিক দেবতা অ্যাপেলাে, জিউস, ব্যাকারের প্রাণবন্ত, পেশিবহুল, কুতিকেশ মূর্তির অনুকরণ গান্ধার শিল্পের বিষয়বস্তু হয়ে ওঠে। গ্রিক শরীর সর্বস্বতার সঙ্গে ভারতীয় আধ্যাত্মিকতার আশ্চর্যমিলন। ঘটেছিল এই শিল্পে।
- গান্ধার শিল্পে মূর্তি নির্মাণে সােনালি বা অন্য রংএর গাঢ় প্রলেপ দেওয়া হত এবং ক্ষেত্রবিশেষে মূর্তিতে গোঁফ লাগানাে বা পাগড়ি পরানাের রীতি দেখা যায়।
- দামি অলংকার, উত্তরীয় ও প্রসাধনের ব্যবহারে এই শিল্প নতুন মাত্রা পেয়েছিল। পােশাকের ভাজ পর্যন্তও অনুকরণ করা হয়েছিল।
- শিল্পের আর একটি বৈশিষ্ট্য হল। মসৃণতা ও পুলিশের কাজ।
- বৌদ্ধমূর্তি নির্মাণে গান্ধার শিল্পের প্রভাব সবচেয়ে বেশি। চিন, তিবৃত, মঙ্গোলিয়া, কোরিয়া, জাপান, মধ্য-এশিয়া প্রভৃতি স্থানে কনিষ্কের উদ্যোগে গান্ধার শিল্প জনপ্রিয় হয়ে ওঠে।
গুপ্ত শিল্প রীতি:
গুপ্তযুগে মন্দির নির্মাণকে কেন্দ্র করে শিল্প-স্থাপত্য ও ভাস্কর্যের চরম উন্নতি ঘটে। ড. স্মিথের মতে “স্থাপত্য, ভাস্কর্য ও চিত্রকলা —এই তিনটি শিল্পকলা গুপ্তযুগে। উন্নতির শীর্ষে আরােহণ করেছিল।” অজন্তা, ইলােরা ও উদয়গিরির গুহা মন্দিরগুলির মধ্যে জৈন, বৌদ্ধ ও হিন্দু মন্দির ছিল। কারুকার্যময় বিখ্যাত মন্দিরগুলির গুপ্ত শিল্প মধ্যে দেওগড়ের (ঝাসি) দশাবতারের মন্দির, ভেতরগাঁও-এর (কানপুর)। ইটের মন্দির, কোটেশ্বর, মণিনাগ, সাঁচির মন্দিরগুলিও উন্নত শিল্প স্থাপত্যের পরিচায়ক। এছাড়া সারনাথের বৌদ্ধমূর্তি, অবলােকিতেশ্বর মূর্তি, মথরার ব্রোঞ্জের বৌদ্ধমর্তি ইত্যাদি স্থাপত্যের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। ড. আর. সি. মজুমদার গুপ্তযুগের স্থাপত্যশিল্পকে ভারতীয়দের মৌলিক সৃষ্টি বলেছেন।
পাল ও সেন শিল্প রীতি:
বাংলার সােমপুর, পাহাড়পুর, ওদন্তপুর, বিক্রমশীলা প্রভৃতি মহাবিহারের স্থাপত্য, ভাস্কর্য এবং চিত্রশিল্প শিল্প-স্থাপত্যের অনন্য দৃষ্টান্ত। বিভিন্ন বিহার ও মন্দির নির্মাণকৌশল তিবৃত ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সুবর্ণভূমির শিল্পপ্রেমীরা অনুকরণ করে। বাস্তশিল্পে ‘সর্বতােভদ্র’ নামে একপ্রকার মন্দির নির্মাণ রীতির উল্লেখ আছে। ড. নীহাররঞ্জন রায় বলেন “পাহাড়পুরের মন্দির প্রাচীন বাংলার শ্রেষ্ঠ বিস্ময়। সকল সর্বতােভদ্র মন্দিরের পুরােভােগে এর অবস্থান দেখা যায়।” স্থাপত্যের জগতে এটি উল্লেখ্য।
টেরাকোটা শিল্প রীতি:
পালযুগের ‘টেরাকোটা শিল্প’ (বা পােড়ামাটির মূর্তি ও সূক্ষ্ম কারুকার্যময় শিল্প) স্থাপত্য শিল্পের মৌলিক প্রতিভার পরিচয় বহন করে। বিখ্যাত দুই স্থাপত্যশিল্পী ছিলেন স্বীয় ও তার ছেলে বীতপাল। সমসাময়িক একটি লিপিতে সােমপুরী মহাবিহারের শিল্পরীতি সম্পর্কে বলা হয়েছে, “জগতের নয়নের একমাত্র বিরামন্থল অর্থাৎ দর্শনীয় বস্ত।” পালযুগে অষ্টধাতুর ও কালােপাথরের তৈরি দেবদেবীর মূর্তিগুলি সৃজনশীলতার পরিচয় দেয় মূল্যবান কষ্টিপাথরের তৈরি বহু মূর্তি পালদের ভাস্কর্যের সাক্ষা- বহন করে।বিভিন্ন ভঙ্গির নারীমূর্তি ও দেবদেবীর মূর্তি পােড়ামাটির ফলকে সুন্দরভাবে খােদাই করা আছে। সেনযুগে বহু খ্যাতনামা শিল্পীর উদ্ভব ঘটেছিল। এঁদের মধ্যে বরেন্দ্রভূমির শূলপাণি উল্লেখ্য। অন্য শিল্পীদের মধ্যে কর্ণভদ্র, বিষ্ণুভদ, তথাগতসাগর, সুত্রধর প্রমুখের শিল্প প্রতিভা প্রশংসার দাবি রাখে। বল্লালসেনের ‘বল্লালবাড়ি’ স্থাপত্যশিল্পের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।
পল্লব শিল্প রীতি:
পল্লব রাজাদের আমলে প্রথমত, স্থাপত্য ও ভাস্কর্যশিল্পে ধর্মকেন্দ্রিকতা লক্ষ করা গেলেও অসম্ভব শৈল্পিক নৈপুণ্যে তা আজও চিরভাস্বর হয়ে আছে।
দ্বিতীয়ত, সূক্ষ্ম কারুকার্যময় মন্দির স্থাপত্যই পল্লব শিল্পের অন্যতম বৈশিষ্ট্য।
তৃতীয়ত, পল্লব শিল্পের আর একটি বৈশিষ্ট্য হল পাহাড় কেটে মন্দির নির্মাণের রীতি। ড. সরসীকুমার সরস্বতীর মতে, অমরাবতী শিল্পকলার প্রভাব পল্লব শিল্পের মধ্যে লক্ষ করা যায়। পল্লব শিল্পের ক্রমবিবর্তনের ধারা ধরে এই শিল্পকে মােট চারটি শিল্পরীতিতে ভাগ করা যায়। যেমন— মহেন্দ্র শিল্পরীতি,
মহামল্ল বা নরসিংহ শিল্পরীতি, রাজসিংহ বা দ্বিতীয় নরসিংহ শিল্পরীতি ও অপরাজিত শিল্পরীতি। পল্লবরাজ প্রথম মহেন্দ্রবর্মন (৬০০-৬২৫ খ্রিঃ) পাহাড় কেটে মন্দিরের রূপদানের কৌশল প্রথম আবিষ্কার করেন। পাহাড় কেটে সুন্দরভাবে বাঁকানাে পিলার, চক্রাকার লিঙ্গম ও অসাধারণ কারুকার্যময় গােপুরম বা তােরণ তার সময় নির্মিত হয়। পল্লব শিল্পের শ্রেষ্ঠ নিদর্শনগুলির মধ্যে ‘একাম্বরনাথ মন্দির’, ‘মুক্তেশ্বর মন্দির’, ‘বৈকুণ্ঠ পেরুমল মন্দির’, ‘ঐরাবতেশ্বর মন্দির, ‘ত্রিপুরান্তকেশ্বর মন্দির’, ‘মামল্লপুরমের মন্দির, মহাবলীপুরমের সপ্তরথের মন্দির’ (সপ্ত পাগােড়া পাঁচটি রথ পঞ্চপাণ্ডবের নামে এবং দ্ৰৌপদী ও গণেশ রথ মন্দির) ও কারি কৈলাসনাথের মন্দির’ উল্লেখ্য। অধ্যাপক ড. নগেন্দ্রনাথ ঘােষ শেষ মন্দিরদ্বয় সম্পর্কে বলেন ‘the Pallava art is more evalued and more elaborate‘।
চোল ও দ্রাবিড় শিল্প রীতি:
‘কালিঙ্গ থুপারনি’, ‘জীবক চিন্তামণি’ ইত্যাদি গ্রন্থে চোল শিল্পের বহ তথ্য রয়েছে। স্থাপত্য-ভাস্কর্য শিল্পের ক্ষেত্রে চোলদের অসামান্য অবদান ছিল। ‘দ্রাবিড় শিল্পরীতি’তে গেল স্থাপত্য নিদর্শনগুলি তৈরি হয়েছিল। এর উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হল ইলােরার কৈলার্স মন্দির যা রাষ্ট্রকুটরাজ প্রথম কৃষ্মের (৭৫৮-৭৭২) তৈরি। সুবর্ণভূমির শৈলেন্দ্র-রাজা শ্রীবিজয় রাজরাজ চোলের অনুমতিক্রমে নেগাপত্তমে একটি বৌদ্ধ মন্দির নির্মাণ করেছিলেন। প্রথম দিকে চোল রাজারা ক্ষুদ্রাকৃতির মন্দির তৈরি করলেও পরবর্তীকালে বিশালাকৃতির মন্দির তৈরি করে। সুক্ষ্ম কারুকার্যময় বৃহদাকার তােরণ বা ‘গোপুরম’ বা প্রবেশদ্বার চোল শিল্পের বিস্ময়কর বৈশিষ্ট্য। কুম্ভকোনমের গােপুরমটি স্থাপত্যশিল্পের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। চোল শিল্পের বিখ্যাত নিদর্শনগুলির মধ্যে চোলরাজ বিজয়ালয়ের ‘চোলেশ্বর মন্দির’, প্রথম পরান্তকের ‘করনাথের মন্দির’, প্রথম বাজরাজের তাঞ্জোরের ‘রাজরাজেশ্বরের মন্দির’, প্রথম রাজেন্দ্র চোলের ‘গঙ্গাইকোণ্ড চোলপুরমের মন্দির’, ‘সুব্রাত্মণ্য মন্দির’ ও ‘দ্বারসমুদ্রের মন্দির’ ইত্যাদি।
এছাড়া চালুক্য রাজাদের এলিফ্যান্টা দ্বীপের মন্দির স্থাপত্য উল্লেখযােগ্য। বল্লাল সেনের রাজশাহির দেওপাড়ার প্রদ্যুম্নেশ্বরের মন্দির, গঙ্গরাজ অনন্তদেব চোড়গঙ্গোর (১০৭৮১১৫০) পুরীর জগন্নাথ মন্দির, গঙ্গরাজ প্রথম নরসিংহের (১২৩৮-১২৬৪) কোনারকের সর্যমন্দির, লিঙ্গরাজ মন্দির, মুক্তেশ্বর মন্দির তৈরি হয় উত্তর ভারতের নাগররীতি’তে। সর্যমন্দিরকে দূর থেকে কৃষ্ণবর্ণের মতাে দেখতে বলে একে ‘কৃষ্ণ প্যাগােডা’বলে। আবুপাহাড়ে শ্বেতপাথরের জৈনমন্দির ও মধ্যপ্রদেশের চান্দেল্লরাজ প্রথম বঙ্গ (৯৫৪-১,০০২) ও পরবর্তী রাজাদের চেষ্টায় ১১৫০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে খাজুরাহাের ত্রিশটি মন্দির তৈরি হয়।