রাষ্ট্রের উৎপত্তি: বিবর্তনবাদ বা ঐতিহাসিক মতবাদ: Evolution or historical theory
ভূমিকা:
রাষ্ট্রের উৎপত্তি মানবসভ্যতার অন্যতম প্রাচীন ও জটিল প্রশ্ন। রাষ্ট্র কিভাবে সৃষ্টি হয়েছে, সেই প্রশ্নের উত্তর একক কোনো তত্ত্বে পাওয়া যায় না। তবু বিভিন্ন মতবাদের মধ্যে বিবর্তনবাদ বা ঐতিহাসিক মতবাদই রাষ্ট্রের উৎপত্তি সম্পর্কে সর্বাধিক গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত। অধ্যাপক গার্নারের মতে, রাষ্ট্র ঈশ্বরের সৃষ্টি নয়, পশুশক্তির ফল নয়, কোনো সামাজিক চুক্তির ফল নয় এবং পরিবারের সরল সম্প্রসারণও নয়; বরং দীর্ঘকাল ধরে মানবসমাজের নানা উপাদানের ধারাবাহিক ক্রমবিকাশের ফলে আধুনিক রাষ্ট্রের জন্ম হয়েছে। বিবর্তনবাদ অনুসারে রাষ্ট্র কোনো নির্দিষ্ট মুহূর্তে সৃষ্ট নয়, বরং মানবসমাজের অভ্যন্তরীণ প্রয়োজন, সংঘাত, উন্নতি ও চাহিদার ক্রমবিকাশের ফলাফল।
রাষ্ট্রের উৎপত্তিতে বিবর্তনের বিভিন্ন উপাদান:
রক্তের সম্পর্ক:
বিবর্তনবাদ অনুসারে রক্তের সম্পর্ক রাষ্ট্রগঠনের প্রথম ভিত্তি। রক্তের সম্পর্ক থেকেই পরিবারের জন্ম, যা মানবসমাজের প্রাচীনতম প্রতিষ্ঠান। পরিবার বড় হতে হতে গোষ্ঠী, গোষ্ঠী বড় হতে হতে উপজাতি এবং উপজাতি থেকে বৃহত্তর সামাজিক একতার উদ্ভব ঘটে। পরিবারে পারস্পরিক নির্ভরতা, সুরক্ষা ও সহযোগিতার যে ঐতিহ্য তৈরি হয়, তা ধীরে ধীরে বৃহত্তর সমাজব্যবস্থায় বিস্তৃত হয়ে রাষ্ট্রগঠনের পথ প্রশস্ত করে।
ধর্ম:
ধর্ম প্রাচীন সমাজে এক শক্তিশালী ঐক্যবন্ধন হিসেবে কাজ করেছে। ধর্মীয় বিশ্বাস মানুষকে একত্রিত করে, সামাজিক নিয়ম-কানুন মেনে চলতে সহায়তা করে এবং পুরোহিত শ্রেণির মাধ্যমে সামাজিক নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে। মার্কিন রাষ্ট্রনায়ক উড্রো উইলসনের ভাষায়—
“রক্তের সম্পর্ক ছিল প্রতীক, আর ধর্ম ছিল ঐক্য, পবিত্রতা ও আনুগত্যের বাহন।”
ধর্ম মানুষের নৈতিকতা, কর্তব্যবোধ এবং কর্তৃত্বস্বীকারের মানসিকতা তৈরি করে, যা রাষ্ট্রগঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।
যুদ্ধবিগ্রহ ও সংঘাত:
বিবর্তনবাদ রাষ্ট্রগঠনে যুদ্ধের ভূমিকাকে বিশেষ গুরুত্ব দেয়। প্রাচীন যুগে এক গোষ্ঠীর সঙ্গে আরেক গোষ্ঠীর সংঘর্ষ ছিল স্বাভাবিক ঘটনা। দুর্বল গোষ্ঠীকে সুরক্ষা দিতে শক্তিশালী নেতা উদ্ভূত হয় এবং ধীরে ধীরে কেন্দ্রীয় কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা পায়। যুদ্ধের ফলে নতুন ভূখণ্ড দখল, নতুন নেতৃত্বের উত্থান এবং বৃহত্তর রাজনৈতিক সংগঠনের সৃষ্টি হয়। আধুনিক যুগেও রাষ্ট্র-রাষ্ট্র যুদ্ধের ফলে নতুন রাষ্ট্রের জন্ম হয়েছে, যা যুদ্ধের ঐতিহাসিক গুরুত্বকে নির্দেশ করে।
অর্থনৈতিক চেতনা:
মানবসভ্যতার এক পর্যায়ে সম্পত্তির ব্যক্তিগত মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হয়। এই ব্যক্তিগত সম্পত্তি রক্ষা করার জন্য উৎপাদক বা মালিক শ্রেণি একটি সাংগঠনিক শক্তির আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়। ফলে নিরাপত্তা, সুরক্ষা এবং সম্পত্তির অধিকার রক্ষার প্রয়োজনীয়তা রাষ্ট্রের উদ্ভবের পথে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। মার্কসবাদীরা বিশেষভাবে মনে করেন—রাষ্ট্র হলো অর্থনৈতিক অসমতার ফল, যেখানে শাসকশ্রেণির স্বার্থ রক্ষাই রাষ্ট্রের মূল লক্ষ্য।
রাষ্ট্রনৈতিক বা রাজনৈতিক চেতনা:
শিক্ষা, অভিজ্ঞতা ও জীবনযাপন মানুষকে রাজনৈতিক চেতনার দিকে ধাবিত করে। মানুষ বুঝতে পারে সমাজে শৃঙ্খলা রক্ষা, ন্যায় প্রতিষ্ঠা, শান্তি বজায় রাখা এবং সংঘাত নিয়ন্ত্রণের জন্য একটি স্থায়ী কর্তৃত্ব প্রয়োজন। এই উপলব্ধিই রাষ্ট্রের মানসিক ভিত্তি গড়ে তোলে। রাজনৈতিক সচেতনতা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে নেতৃত্ব, আইন, বিধি-নিষেধ, শাসনব্যবস্থা ও প্রশাসনের প্রয়োজন অনুভূত হয়, যার চূড়ান্ত রূপই রাষ্ট্র।
মূল্যায়ন:
বিবর্তনবাদ বা ঐতিহাসিক মতবাদ রাষ্ট্রের উৎপত্তি ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে সর্বাধিক বৈজ্ঞানিক ও বাস্তবভিত্তিক মতবাদ। এই মতবাদ কোনো অলৌকিক ব্যাখ্যা, চুক্তি বা কল্পিত উপাখ্যানের উপর দাঁড়িয়ে নয়; বরং সমাজবিজ্ঞান, ইতিহাস, নৃতত্ত্ব ও অর্থনীতির উপর ভিত্তি করে। রাষ্ট্র কোনো নির্দিষ্ট দিনে, নির্দিষ্ট ঘটনার ফলে বা নির্দিষ্ট ব্যক্তির উদ্যোগে সৃষ্টি নয়; বরং মানবসমাজের ক্রমাগত পরিবর্তন, অভিজ্ঞতা, সংঘর্ষ, উন্নয়ন ও প্রয়োজনের মাধ্যমে ধীরে ধীরে গঠিত হয়েছে। তাই ঐতিহাসিক মতবাদ রাষ্ট্রের জন্মকে বাস্তবসম্মত ও বৈজ্ঞানিকভাবে ব্যাখ্যা করে।
উপসংহার:
সারসংক্ষেপে বলা যায়, রাষ্ট্রের উৎপত্তি কোনো একক তত্ত্বের মাধ্যমে ব্যাখ্যা করা যায় না। কিন্তু বিবর্তনবাদ রাষ্ট্রের জন্মকে বহুমাত্রিক দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যাখ্যা করে, যা সর্বাধিক গ্রহণযোগ্য। পরিবার, ধর্ম, যুদ্ধ, অর্থনীতি, রাজনৈতিক চেতনা—এই সকল উপাদানের যৌথ অবদানেই প্রাচীন সমাজ থেকে আধুনিক রাষ্ট্রের সৃষ্টি হয়েছে। তাই রাষ্ট্র মানবসমাজের ধারাবাহিক বিবর্তনের একটি অপরিহার্য ফল।
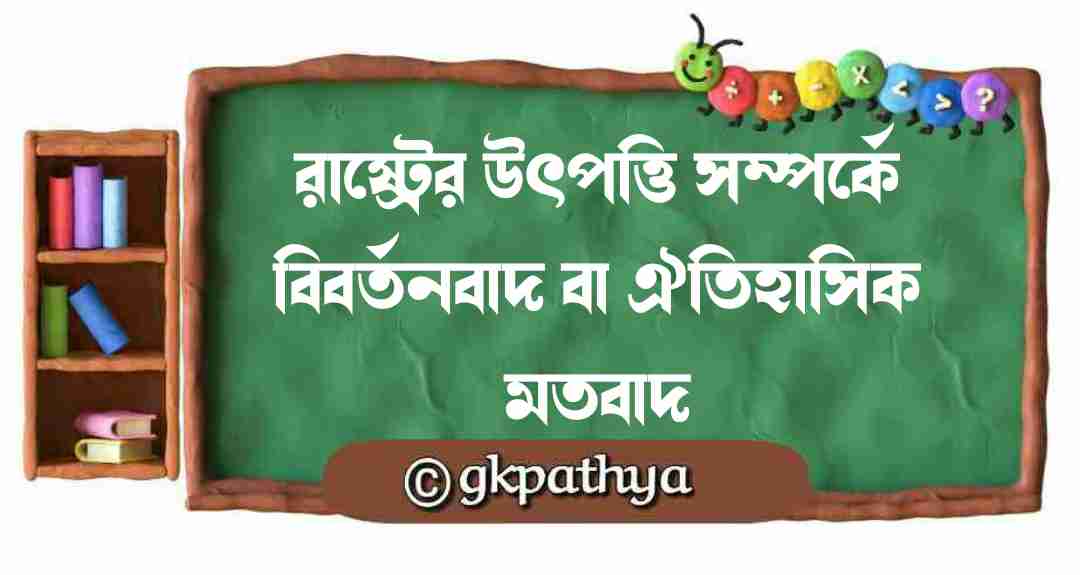
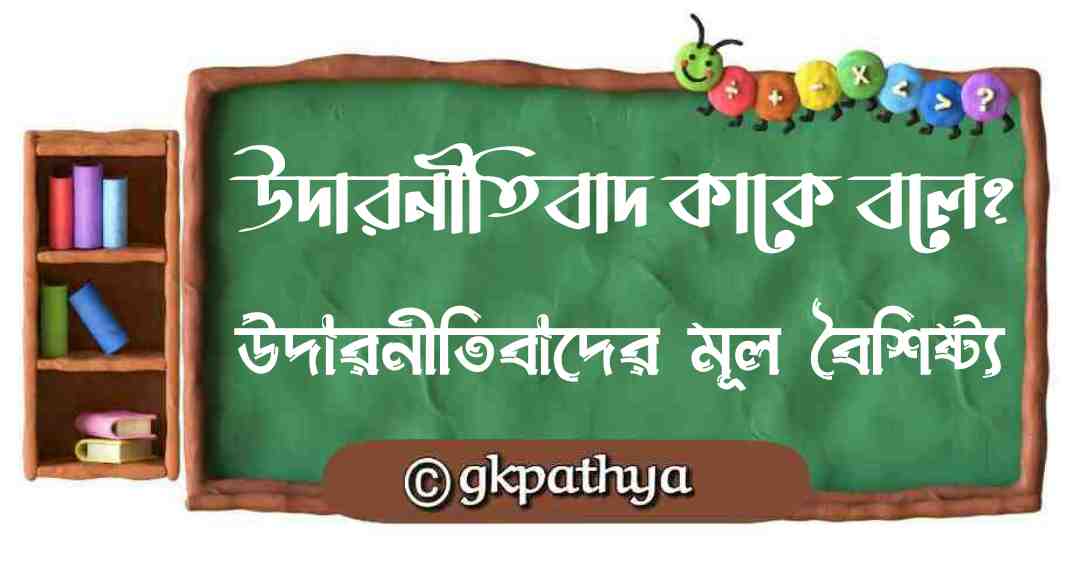
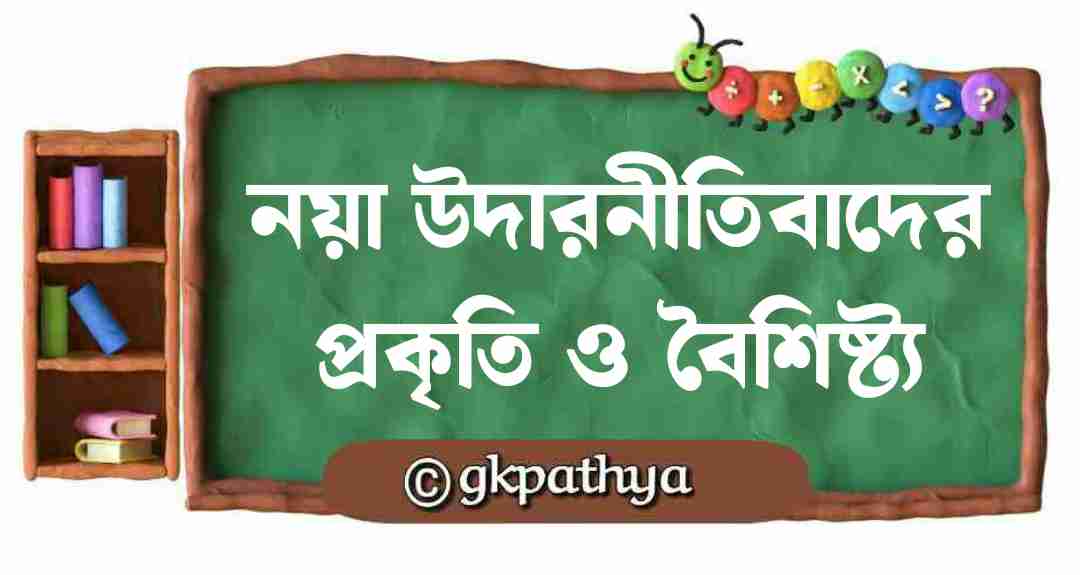

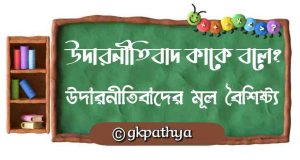
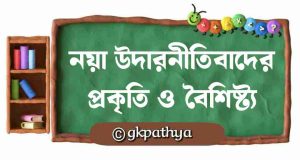

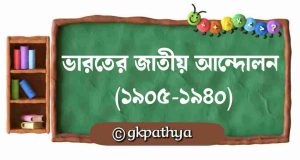
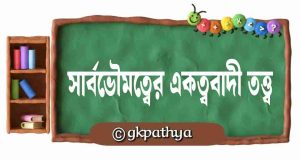
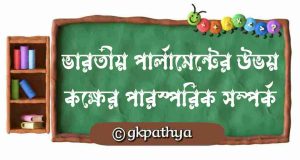
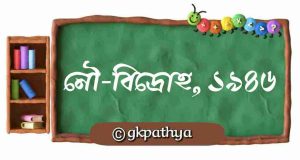


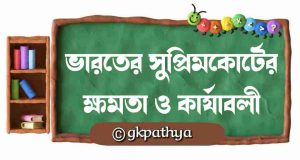
Post Comment